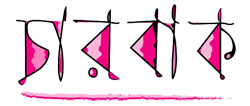“কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।
রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব যার হাতে মরণ বাঁচন।
আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে শিশু রবি শশী দোলে;
(মায়ের) একটুখানি রূপের ঝলক স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন।
পাগলী মেয়ে এলোকেশী নিশীথিনীর দুলিয়ে কেশ,
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায় লীলার যে তার নাইকো শেষ।
সিন্ধুতে মার বিন্দু খানিক, ঠিকরে পড়ে রূপের মানিক;
বিশ্বমায়ের রূপ ধরে না— মা আমার তাই দিগ্ বসন।”
— নজরুল ইসলাম।
পাগলী মেয়ে এলোকেশী নিশীথিনী…
১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ‘ইনষ্টিটিউট অফ্ হিষ্টোরিক্যাল ষ্টাডিজ’ সংস্থার বার্ষিক সম্মেলনে ‘A contribution to the history of the Indian labouring class through the ages : Problems and movements’ শীর্ষক আলোচ্য বিষয়টির উপর অনেকগুলি ‘পেপার’ জমা পড়ে ও বিতরণ করা হয়। তন্মধ্যে একটি পেপারের শীর্ষক ছিল ‘Black movements of the Indian labouring class : Goddess Kali’. পেপারটি জমা দিয়েছিলেন শ্রী বিমানবিহারী মাইতি। অধিবেশনে তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও পেশ করেছিলেন। ভারতের শ্রমজীবী জনগণের ইতিহাসের প্রতি তাঁর ঐ নতুন ‘অ্যাপ্রোচ’ উপস্থিত পাঠক-শ্রোতাদের বিস্মিত করেছিল। ভারতের ইতিহাস অধ্যয়নের যে পদ্ধতি তাঁর পেপারে অনুসৃত হয়েছিল, তা ছিল অভিনব। ঐ পদ্ধতি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অধ্যয়নের এক নতুন দিগন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে।
ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে পুরাণাদি পাঠ করে সম্প্রতি জানা গেছে যে, ভারতের ইতিহাস অধ্যয়নের অনুসৃত ঐ পদ্ধতিটি সঠিক। একমাত্র ঐভাবে এগোলেই প্রাচীন ভারতীয় চরিত্রগুলিকে অর্থাৎ শিব দুর্গা কালী শ্যামা ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র বরুণ রাম কৃষ্ণ ভৃগু দক্ষ প্রমুখ চরিত্রগুলিকে যথার্থভাবে চেনা যায় ও তাঁদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে যাঁরা ঐ চরিত্রগুলিকে কাল্পনিক বলে মনে করেন, তাঁদের উচিৎ ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ‘ন্যাশনাল হিরো’দের তালিকাটিতে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া। সেই তালিকায় যে সকল ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে তাঁদের মহান কীর্ত্তির জন্য ‘জাতীয় বীর’-এর মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই ও সম্রাট আকবর যেমন স্থান পেয়েছেন, তেমনি সগৌরবে স্থান পেয়েছেন শিব রাম কৃষ্ণ প্রমুখেরাও। অর্থাৎ কিনা এঁরা কেবল ‘মূর্খ’ জনগণের মস্তিষ্কে বিরাজ করছেন তা নয়, সরকারিভাবেও স্বীকৃত।
আমাদের প্রয়োজন শ্যামাকে নিয়ে। নজরুল ইসলাম হঠাৎ কেন শ্যামাসঙ্গীত লিখতে-গাইতে গেলেন, তার রহস্য আমাদেরকে জানতে হবে। আমরা বুঝতে চাই, তাঁর এই আচরণের যাথার্থ্য কী? ‘শ্যামা’ ধারণার উদ্ভব ও তার ঐতিহাসিক বিকাশধারার বিশেষ এক ক্ষণে, আমরা কেন দেখছি যে, সেই ধারণা নজরুলের মত একজন কবির মনের মণিকোঠা জুড়ে বসে গেল এবং শ্যামাসঙ্গীত হয়ে প্রকাশিত হল তাঁর মাধ্যমে? নজরুলই বা কেন তাঁকে মনের মণিকোঠায় লালন করে তৃপ্তি পান, সৃষ্টির আনন্দ পান? ঐ বিশেষ কালখণ্ডে, কোন অমোঘ নিয়মে, নজরুল ও শ্যামাসঙ্গীত যথাক্রমে আধার-আধেয় হবার ভবিতব্য এড়াতে অক্ষম হয়? আর সেজন্যেই, আমাদের সর্ব্বাগ্রে জানতে হবে শ্যামাকে। কিন্তু জানতে হলে তো ভারতের ইতিহাস পড়তে হয়। প্রশ্ন হল : ভারতের ইতিহাস কোন্টি এবং কীভাবে তা পাঠ করা হবে? সেটি নির্ণয় করে নিয়ে তবেই আমরা ইতিহাসের পাতা থেকে শ্যামাকে উদ্ধার করতে পারি। সংক্ষেপে সেই কাজটি আগে সেরে ফেলা যাক।
বেদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত তন্ত্রাদি জয়াক্ষ গ্রন্থগুলিকে আধুনিক ঐতিহাসিকরা ভারতের ইতিহাস রূপে স্বীকৃতি দেন না। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা’ প্রবন্ধে ঐগুলিকেই ইতিহাসের মর্য্যাদা দিয়েছেন। তাঁর সুস্পষ্ট উক্তি এই প্রকার যে, ‘আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে, কিন্তু ইহা যথার্থই আর্য্যদের ইতিহাস।’ আর, ইউরোপীয় চিন্তার ছাঁচে ফেলে আমরা যাতে এই সকল ইতিহাস গ্রন্থ না পড়ি, তাই তিনি পরিষ্কারভাবে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, ‘ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জ্জন না করিলেই নয়।’ ভারতের ইতিহাসের এইরূপ গ্রন্থনির্দ্দেশ ও গ্রন্থপাঠপদ্ধতির নির্দ্দেশ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ করে যাওয়া সত্ত্বেও তথাকথিত রবীন্দ্রভক্ত ঐতিহাসিক সাহিত্যিকরা কেউই তাঁর নির্দ্দেশ মান্য করেননি। এ ব্যাপারে তাঁরা প্রায় সকলেই রবীন্দ্রবিরোধী।
তবে সেই রবীন্দ্রবিরোধিতার কথাটা তাঁরা স্পষ্ট করে বলতে ভয় পান। অনেকে আবার একটু ক্ষমাঘেন্নার মনোভাব নিয়ে চলেন। ভাবখানা এইরকম যে, ‘লোকটার তো কোন অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন ছিল না, দু-চারটা ভুল বলতেই পারে; ক্ষমা-ঘেন্না করে নেওয়াই ভাল।’ এই সকল হিপোক্রিটদের প্রতি বিধির পরিহাস বড়ই নিষ্ঠুর! বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে বঙ্গের নিপীড়িত আত্মা যে দু-জনের মাধ্যমে নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ করেছিল, দু-জনেরই কার্য্যত কোন অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন ছিল না।
ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিচারে তাঁরা ছিলেন মূর্খ— একজন রবীন্দ্রনাথ, অন্যজন নজরুল। দেখা যাচ্ছে, যন্ত্রণাকাতর মানুষ যেমন ‘উঃ আঃ’ আওয়াজ করে যন্ত্রণা লাঘব করার চেষ্টা করে, সে যুগের বঙ্গমানস তেমনি সেই রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্য-সাহিত্য প্রকাশের মাধ্যমে আপন যন্ত্রণা লাঘব করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। এমনকি আজও, অ্যাকাডেমিশিয়ানদের বন্ধ্যাভূমি থেকে জীবনীশক্তি না পেয়ে তথাকথিত শিক্ষাজগৎ ঐ রবীন্দ্রনাথ নজরুলের নিকট থেকেই জীবনীশক্তি আহরণ করে থাকে। সুতরাং রবীন্দ্রনির্দ্দেশিত উক্ত জয়াক্ষ গ্রন্থগুলিকেই আমরা ইতিহাস জ্ঞানে পাঠ করব।
ইতিহাস অধ্যয়নের অপর একটি ধারার কথা বলে নিয়ে আমরা সরাসরি আমাদের বিষয়সীমায় ঢুকে পড়ব। তথাকথিত বস্তুবাদী ঐতিহাসিকদের এঙ্গেলস বলে গিয়েছিলেন— “… (মর্গ্যানের তথ্যানুসারে) আত্মীয়তাবিধি হচ্ছে নিষ্ক্রিয়, পরিবারের অগ্রগতি তাতে লিপিবদ্ধ হয় বহু দীর্ঘ ব্যবধানের পরপর। … মার্কস এর সঙ্গে যোগ করেছেন, এই একই কথা রাজনীতি আইন ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ক পদ্ধতি সম্পর্কেও সাধারণভাবে প্রযোজ্য।”১ অর্থাৎ কিনা সমাজমানসের বিবর্ত্তন, উৎপাদন ব্যবস্থার বিবর্ত্তনের পিছু পিছু হাঁটে।
যথা, সমাজে ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভব হয়ে গেলেও সমাজমানসে যৌথবোধের বিবর্ত্তন চলে আরও বহুদিন ধরে। একালে যেমন অনেকে এখনও ‘ষোল আনা সত্যি’ কথাটি বলে থাকেন, যদিও আনা-পয়সার ব্যবস্থাটি কবেই উঠে গেছে। একই নিয়মে সেকেলে বাঙালীরা এখনও ‘পাঁচ-নয়া’, ‘দশ-নয়া’ বলে থাকেন। ভারত সমাজে যখন ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, সমাজমানসে তখন স্বভাবতই রাজত্ব চলছিল যৌথব্যবস্থার বোধের। আর ভারতের ইতিহাস যখন শ্রুতিবাহিত হয়ে উত্তরসূরীদের মাথায় চাপতে শুরু করে, সেই প্রাচীন ভারতীয় সমাজে, তখনও, ব্যক্তিমালিকানার চিহ্ণ পর্য্যন্ত নেই, কী সমাজের কর্ম্মজগতে, কী ভাবজগতে। যেহেতু ব্যক্তিমালিকানা নেই, তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নেই। ফলে ব্যক্তিনামের প্রচলনও হয়নি, সবই যৌথ।
তবে, একসময় যৌথসমাজ ভাঙতে আরম্ভ করে। শুরুতে ‘সমগ্র’ ভেঙেছে কতগুলি বড় বড় খণ্ডে। একেবারে কণায় পরিণত হয়ে non-divisible বা individual-এ পরিণত হতে কয়েক যুগ খরচ হয়ে গেছে। অথচ আধুনিক ঐতিহাসিক প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে গিয়ে প্রথমেই খোঁজেন ব্যক্তিকে; নাম, বাবার নাম, পদবী, রাজ্যের নাম ইত্যাদি তাঁকে পেতেই হবে। গরু হোক আর বিদ্যাসাগরই হোক, তাকে এনে শ্মশানে ফেলা চাই। কেবল শ্মশানের কথাই যে জানা আছে। সমাজ সম্পর্কিত তাঁর বর্ত্তমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণার সঙ্গে ঐ প্রাচীন সমাজের সমস্ত বর্ণনাকে খাপ খেতেই হবে। অন্যথায় সেগুলি ‘রূপকথা’ মাত্র।
এই সহজ কথাটি ঐ ঐতিহাসিকদের মস্তিষ্কে কিছুতেই ঢোকে না যে, যৌথসমাজের মানুষের সাংস্কৃতিক চিন্তাশৃঙ্খলা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষের চিন্তাশৃঙ্খলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং সেটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। প্যারাডাইমটাই বদলে গেছে পরবর্ত্তী যুগে। সুতরাং যৌথচিন্তাশৃঙ্খলায় নিজেকে উন্নীত না করে তাদের বর্ণনাকে বুঝতে চেষ্টা করা বৃথা। আর মানুষ যেহেতু স্বভাবতই ‘ঝাঁক-জীব’ এবং আদিম সাম্যবাদী ভারতসমাজ তারই এক নিবিড় রূপ, তাতে intuition, আবেগ ও হৃদয়ের অধিক শাসন স্বাভাবিক ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘স্কুলের পাঠ্যগ্রন্থ বহির্ভূত সেই ভারতবর্ষের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করে’ তবেই তাকে বুঝতে হবে।
রবীন্দ্রনাথ ও মার্কসকে মাথায় রেখে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পাঠ করলে শ্যামার যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়, এবার তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থিত করা যাক। ঐ সকল গ্রন্থের বহুরৈখিক বর্ণনার কেবলমাত্র সমাজবিষয়ক রেখাটি অনুসৃত হলে যেরূপ অর্থ দাঁড়ায়, প্রথমে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। তারপর ঐ বর্ণনার জগৎ বিষয়ক রেখাটি অনুসরণ করা হবে।
প্রাচীন ভারতের ঐ বর্ণনায় ‘সমগ্র জনসাধারণ’কে ‘একীভূত সমাজদেহ’ ধরে তার নামকরণ করা হয়েছে ‘মহামায়া’। যখন মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই, সবই ‘অবিশেষ’, দেহে মনে সব দিক থেকেই মানুষ সমান, ঝাঁকবদ্ধ প্রাণী-প্রজাতির মত, সেই আদিম সাম্যবাদী মানবসমাজকে বলা হয়েছে, ‘বহু হস্তপদ বিশিষ্ট স্থূল জলজন্তুর মত মহামায়া’। আদিতে সেই মহামায়াই ছিল, ‘আর কিছুই ছিল না’।২
বলা হয়েছে, তারপর তার থেকে শিবের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ কিনা ‘সমগ্র জনসাধারণ’ (মহামায়া) থেকেই আদি পরিচালক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। পুরাণাদিতে তাকে ‘মহান’ শব্দে চিহ্ণিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মহান ‘প্রজাপতি পদবাচ্য, কিন্তু প্রজাপতি নহে।’ অর্থাৎ, তখনও সমাজ বিভাজিত হয়নি। পরিচালকের আবির্ভাব ঘটে গেলেও সেই পরিচালক পরিচালিতের সঙ্গে প্রেমবন্ধনে গভীরভাবে বদ্ধ। শুধুমাত্র সমাজের সদস্যগণ ‘গুণবৈষম্য’ অর্জ্জন করেছে। পরিচালক-পরিচালিতের এইরূপ যৌথ সামাজিক অস্তিত্বকে অর্দ্ধনারীশ্বর, ব্রহ্মময়ী, বুড়াশিব, প্রণবস্বরূপিণী, মহাকাল, পরমাপ্রকৃতি, অংরূপিণী, বিন্দুরূপিণী ইত্যাদি নানা নামে চিহ্ণিত করা হয়েছে।
সমাজের সুস্পষ্ট বিভাজন হতে সুদীর্ঘ সময় ব্যয়িত হয় এবং সমাজমানসে তার প্রতিচ্ছবি আমরা পাই আরও অনেক পরে। প্রথম স্পষ্ট বিভাজন-স্বরূপ দেখা যায় জ্ঞানজীবী (মহর্ষিগণ ও প্রজাপতিগণ) ও তাঁদের অনুসরণকারী শ্রমজীবী (সম্প্রদায়) রূপে; তারও অনেক পরে তাদের বিবর্ত্তন ঘটে জ্ঞানজীবী পণ্যজীবী ও শ্রমজীবী অর্থাৎ যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন শ্রেণীতে সমাজটা ফেটে যায়। পরে আরও সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা টানা হয়। জ্ঞানজীবী ও তাদের নেতৃস্থানীয়দের যথাক্রমে ব্রহ্মাণী ও ব্রহ্মা, পণ্যজীবী ও তাদের নেতৃস্থানীয়দের বৈষ্ণবী ও বিষ্ণু, এবং শ্রমজীবী৩ ও তাদের নেতৃস্থানীয়দের মহেশ্বরী ও মহেশ্বর নামে চিহ্ণিত করা হয়। …
এই বিভাজন বাড়তে বাড়তে জ্ঞানজীবী ও পণ্যজীবীদের অর্থাৎ যথাক্রমে অসুর ও দেবতাদের বিশাল বংশ (সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ) গড়ে ওঠে এবং ক্ষমতা (স্বর্গ) দখলের জন্য শুরু হয়ে যায় দেবাসুর সংগ্রাম। ঐ ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে মহেশ্বর ও মহেশ্বরীর ভূমিকা হয় ব্যবহৃত হয়ে যাওয়ার ভবিতব্য। অবশ্য মহেশ্বর ও মহেশ্বরীর ততদিনে বহু ‘অংশাবতরণ’ ঘটেছে। শ্রমজীবী ততদিনে কৃষিজীবী, কারুজীবী, দারুজীবী, বারুজীবী ইত্যাদি নানা রূপে বিভাজিত। তাই তখন তার নানা নামও দেওয়া হয়ে গেছে; যথা, সতী, পার্ব্বতী, দুর্গা, চণ্ডী, কালী, তারা ইত্যাদি এবং শ্যামা। কার্য্যত কর্ম্মীজনগণের ক্রমবিকাশের (ক্রম অধঃপতনের) ইতিহাসটা মহামায়া থেকে সতী পার্ব্বতী দুর্গা চণ্ডী দশ-মহাবিদ্যা হয়ে শেষমেষ শ্যামায় এসে ঠেকেছে।
মহামায়া থেকে সকলেরই জন্ম অর্থাৎ কিনা ‘সমগ্র জনসাধারণ’ থেকেই বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলির জন্ম হয়েছে, আধুনিক ভাষা পদ্ধতিতে যাদের আমরা বলি— সরকারী কর্ম্মচারী, শিক্ষিত জনগণ, মারমুখী জনতা, বিপ্লবী জনগণ, কিংবা নব নব বেসরকারী ক্ষেত্রের কর্ম্মীজনগণ; পৌরাণিক ভাষায় তাদেরই যথাক্রমে পার্ব্বতী, দুর্গা, চণ্ডী, কালী, ও শ্যামা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেই প্রাচীন ভারতীয় ভাষা-পদ্ধতিতে যৌথবয়ানের (ক্রিয়াভিত্তিক-শব্দবিধির) চল প্রচলিত থাকায় শ্রমিক মজদুর ব্যবসায়ী শিক্ষক ছাত্র কেরানী কর্ম্মচারী ইত্যাকার একরৈখিক প্রতীকী (রূঢ়ি) শব্দের ব্যবহার ছিল না, ব্যবহারের কারণও ছিল না বা ঘটেনি। কর্ম্মীজনগণ যখন মারমূর্ত্তি ধরে, আধুনিক বাংলা ভাষায় সাধারণত তাদের বলা হয় ‘ক্ষিপ্ত জনতা’, কিন্তু প্রাচীন বাংলাভাষায় তার নাম চণ্ডী। ‘রণচণ্ডী’ শব্দটি সেই বোধের উত্তরাধিকার আজও বহন করে। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী যখন নেতাদের ক্ষমতাচ্যুত করেন, তখন সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাচীন নাম দুর্গা; (আর সেজন্যই তো, দেশজুড়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যত বাড়বৃদ্ধি হচ্ছে, দুর্গাপূজারও ততই বাড়াবাড়ি হয়ে চলেছে)।
আবার উৎপাদন কর্ম্মজগতের যে অংশ নবোদ্ভূত হয়েছে, এখনও সরকারী স্বীকৃতি পায়নি কিংবা সরকারী আওতার বাইরে নিজের মত চলছে বা চলতে শুরু করেছে, সেই রাষ্ট্রীয় শাসনের বাইরে থাকা বিশাল কৃষিব্যবস্থায় ও কপিলাবস্তু উৎপাদন-কর্ম্মে কর্ম্মরত জনসাধারণকে বলা হত শ্যামা। এই রূপে মহামায়া গৌরী (white) নন, কৃষ্ণ বা কালীও (black-ও) নন, তিনি শ্যামবর্ণা; একালে যার একপ্রকার বোধযোগ্য ধারণা পাওয়া যায় white money, black money, ও grey money তে। স্মর্তব্য যে, শ্যামার (মর্য্যাদাপ্রাপ্ত নয়, কিন্তু নিন্দিতও নয়, নিপীড়িত কিন্তু বিদ্রোহী নয়, এমন জনসাধারণের) পূজা গৃহীও করতে পারেন; কালীর (নিন্দিত জনগোষ্ঠীর) পূজা সাধারণত নিপীড়িত ও বিদ্রোহী বা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরোধী, বিপ্লবী, ও তস্করেরা করে থাকেন, গৃহীরা করতে পারেন না; আর গৌরীর (রাষ্ট্রস্বীকৃত ও মর্য্যাদাপ্রাপ্ত জনসাধারণের) পূজা করেন প্রতিষ্ঠিত ও শাসকের অনুসারী জনসাধারণ। …
বলা হয়েছে, ‘বৈশ্যদিগের সর্ব্বসাধারণের (পণ্যজীবীদের) অভীষ্টদেব সাধারণত জগৎ প্রতিপালক বিষ্ণু’।৪ তেমনি নেতা-ওল্টানো শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর আরাধ্যা দেবী দুর্গা এবং হাভাতে হতদরিদ্র চাষী সহ অবহেলিত কর্ম্মী-জনগণের আরাধ্যা দেবী হলেন মহামায়ার এই শ্যামা-রূপ। কিন্তু প্রশ্ন হল, বৈশ্যরা (পণ্যজীবীরা) কেন বিষ্ণুপূজা করেন, কেনই-বা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী দুর্গাপূজা করেন? এবং অবহেলিত কৃষিজীবী জনসাধারণ শ্যামাপূজা করেন? এর উত্তর হল— ঐরকমই প্রকৃতির বিধান, শাস্ত্রেরও অনুকূল নির্দ্দেশ। সে কী রকম?
প্রকৃতি মানুষের স্বভাবের ভিতরে ঐ ইচ্ছা ঢুকিয়ে রেখেছেন। যে কারণে একালে ক্ষুদে শচীনেরা শচীন তেণ্ডুলকরের ছবি টাঙায়। একই রকম কারণে ক্ষুদে বিষ্ণুরা বিষ্ণুর, ক্ষুদে দুর্গারা দুর্গার এবং ক্ষুদে শ্যামারা শ্যামার ভক্ত (ফ্যান) হয়ে থাকে। যে যার স্বায়ত্বের এলাকা দেখতে পায় তার তার আরাধ্যে। নিজে যা, উঠতে চায় তারই শীর্ষে, তারই Grand, Divine রূপে। এ তো গেল প্রকৃতির বিধানের কথা। মানুষের (সমাজের) বিধান কী? শাস্ত্র বলেন, ‘দেবতা হইয়াই দেবতার পূজা করিবে, স্বয়ং দেবতা না হইয়া দেবতার অর্চ্চনা করিতে নাই।’ (কীভাবে দেবতা হতে হয়, সে সংবাদ অন্যত্র লিখিত হয়েছে)। ‘স্বয়ং বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুপূজা করিবে না, তাহা হইলে সে পূজায় সিদ্ধকাম হইতে পারিবে না।’ ‘রুদ্র না হইয়া রুদ্রপূজা করিবে না।’৪ সম্ভবত এইসব দেখে শুনে রামপ্রসাদ গেয়ে গেছেন— ‘কালী ভেবে, কালী হয়ে, কালী বলে কাল কাটাব।’
কর্ম্মী জনগণের মূর্ত্ত প্রতীকরূপিণী মহামায়ার অংশোদ্ভূতা শ্যামামূর্ত্তির নানা রূপের আরাধনা সেইজন্য কর্ম্মী-জনগণই করে থাকেন। ক্ষমতা দখলাকাঙ্ক্ষী অতি বামেরা যেমন জানেন, ‘জনগণ জনগণ জনগণই শক্তি, জনগণই মুক্তি …’ (তাঁদের সঙ্গীতের একটি অংশ), তেমনি ক্ষমতাধিষ্ঠিত অতি দক্ষিণরাও গণশক্তির মহিমা অনুধাবন করেন এবং ‘হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলমেণ্ট’-এর পিছনে অর্থব্যয় করে থাকেন। আর ভারতীয় মাত্রেই জানেন, পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ নয়, প্রকৃতিই শক্তিরূপিণী। পুরাণাদিতে তাই দেবীর মুখ দিয়ে বলানো হয়— ‘একৈ বাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা …’ — অর্থাৎ, এ জগতে আমি একাই আছি; আমি ছাড়া আর কে আছে? একথা বলে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জনগণ শক্তিরূপে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন।
সেই জনগণ যখন নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত, নানা পেশায় বিভক্ত, তখন তার নানা নাম। ‘লক্ষ্মী সরস্বতী জগদ্ধাত্রী উমা পার্ব্বতী ভারতী অম্বিকা কালী চণ্ডী মহেশ্বরী বারাহী কৌমারী ভগবতী গৌরী ব্রহ্মাণী কাত্যায়নী চামুণ্ডা প্রভৃতি নামে যে সকল দেবীর পূজা ও উপাসনা হয় তা বস্তুত একই মহাদেবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যাও একই দেবীর দশবিধ রূপ।’ অর্থাৎ দেবীর যত রূপ তা সবই কর্ম্মী জনসাধারণেরই রূপ।
দেবীর এই যে এত রকম নাম, এর প্রত্যেকটির পিছনে আছে কোন না কোন সামাজিক সংগ্রাম, আছে বিশেষ কালখণ্ড। প্রত্যেক নামের সঙ্গে তাই এক বা একাধিক কাহিনী ‘মিথ্’-রূপে প্রচলিত রয়েছে, রয়েছে তার ভৌগোলিক অবস্থান ও বাস্তব স্মৃতিচিহ্ণ। ঐ সকল মিথ ও স্মৃতিচিহ্ণ ও তার ধ্বংসাবশেষগুলি থেকে পাওয়া যাবে জনগণের কোন এক গোষ্ঠীর এক বিশেষ কালখণ্ডে ঘটে যাওয়া এক বা একাধিক সংগ্রামের ইতিহাস। একবার ঐ ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর, তার স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে ধর্ম্মীয় আচার রূপে, উৎসবে, ৫ পূজার ধারাবাহিক উত্তরাধিকারে।
নজরুলের সময়কালে ঐ সকল উত্তরাধিকার কোথায় এসে পৌঁছেছিল? বেদপন্থী ও সনাতনপন্থীদের আদি যুদ্ধে (দক্ষযজ্ঞ দ্রষ্টব্য) পরাজিত যৌথসমাজের সনাতনপন্থীরা যবন, ম্লেচ্ছ ও শূদ্র ইত্যাদি নামে চিহ্ণিত হয় ও পালায়, (বেদ পুরাণাদি তন্ত্র থেকে চরকসংহিতা হয়ে Great Exodus পর্য্যন্ত কোথায় সেই ঘটনার স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ নেই?) সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী দেশ যা আর্যাবর্ত্ত্য নামে চিহ্ণিত, সেখান থেকে চারিদিকে তারা ছড়িয়ে পড়ে। সেই সকল পলাতকদের যে সকল ভূখণ্ড আশ্রয় দিয়েছিল, তন্মধ্যে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ (বিহার বাংলা উড়িষ্যা), অন্ধ্র ও মাদ্রাজ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য দেশ অগ্রগণ্য। ‘বৈদিক’-এর বিপরীত ‘তান্ত্রিক’ (দ্র. বঙ্গীয় শব্দকোষ) বলেই এই সমস্ত বেদবিরোধী দেশ তন্ত্র সাধনার উর্ব্বর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। স্মর্তব্য যে, প্রাপ্ত দেড়-শতাধিক তন্ত্রগ্রন্থের মধ্যে ৬৪টি তন্ত্র পাওয়া গেছে শুধু এই বঙ্গদেশ থেকেই। তাই এমনকি বঙ্গদেশের হাওয়াতেও তন্ত্রসাধনার বীজ উড়ে বেড়ায়।
একসময়, এই বিবর্ত্তন পরবর্ত্তী এক যুগে বৌদ্ধরা বেদবিরোধী যুদ্ধে জিতে গিয়ে ষোড়শ মহাজনপদ প্রতিষ্ঠা করলেও, একদিন আবার তাদেরকে হেরে গিয়ে পালাতে হয়। তখনও এই তান্ত্রিক দেশগুলিই তাদের আশ্রয়দাতা হয়ে ওঠে। আর সেই জন্যেই এই ভূখণ্ডগুলির বেশীর ভাগ অধিবাসীকে একযুগে বৌদ্ধ হয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু তাতেও বেদজীবী সৃজিত ‘জন্মদোষে শ্রেণীবিভাজন’-এর নিষ্ঠুর অভিশাপ থেকে জনসাধারণের মুক্তি জোটে না। একদিন এসে হাজির হয় ইসলাম, মুখে তার ‘জন্মদোষে শ্রেণীবিভাজন অস্বীকারের’ সু-উচ্চ ঘোষণা। তান্ত্রিক দেশগুলির বহু মানুষ ভাবেন, এবার বুঝি মিলে যাবে মুক্তি। তাঁরা গ্রামকে গ্রাম মুসলমান হয়ে যান। নজরুলের কালে, তাই দেখা যায়, বঙ্গবাসীদের শতকরা ৬০ জনই মুসলমান; যাঁদের অধিকাংশই আবার নেড়া বৌদ্ধ থেকে ধর্ম্মান্তরিত হয়েছিলেন বলে ‘নেড়ে’ নামে চিহ্ণিত। মুসলমান হয়েও যে নিষ্কৃতি মেলেনি, সেকথা সবাই জানেন।
এই প্রেক্ষাপটে, সাম্যের আহ্বান নিয়ে ভারতে ঢুকল মার্কসবাদের লু-বাতাস— সাম্রাজ্যবাদের পিছু পিছু আগত ‘এনলাইটেনমেণ্ট’-এর হাত ধরে তার আগমন। বাঙালীর মনের মাটি তান্ত্রিক সংগ্রামের বিভিন্ন যুগের মহান যোদ্ধাদের, বৌদ্ধ মুসলমান প্রভৃতি নানা যুগের শহীদদের হাড়ের গুঁড়োয় এমনিতেই যথেষ্ট উর্ব্বর তো ছিলই; সমাজমানসে লোকসংস্কৃতিতে যাপনে সর্ব্বত্র সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রবাহিত অমর্য্যাদা-অসাম্য-নিপীড়নের ও তার প্রতিবাদের ধারাও ছিল অন্তঃসলিলা। তাই ঐ এনলাইটেনমেণ্ট ও মার্কসীয় হাওয়া বইতেই শ্রমিক কৃষক প্রভৃতি নিপীড়িত মানুষদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। নানা রকমের সমিতি, নানা প্রকারের আন্দোলনের ঢেউ উঠতে শুরু করল। প্রাচীন ভারতীয় যুগ থেকে বয়ে আসা নিপীড়িত মানুষের আন্দোলন, আবেগের সমুদ্র পেরিয়ে যুক্তির দ্বীপভূমিতে পা রাখল; আর প্যারাডাইমটাই গেল বদলে।
এই সেই পরিস্থিতি যখন নজরুলের মানসতরু বাংলার ‘সেই মাটি’ থেকে রস টেনে জীবনীশক্তি লাভ করছিল এবং ঠেলে উঠছিল বঙ্গসমাজের মানসলোকের ক্ষুব্ধ আকাশে। বাংলার ‘সেই বায়ু’ থেকে সে তার মানসিক শ্বাসগ্রহণ চালাচ্ছিল, চালাচ্ছিল প্রাণের বিকাশ প্রক্রিয়া। … অবশেষে একদিন যখন বঙ্গের নিপীড়িত আত্মা তাঁরই জিহ্বা লেখনী ও ‘কলজে’টাকে বেছে নিল আত্মপ্রকাশের মাধ্যম রূপে, বেধে গেল এক হুলস্থূল কাণ্ড। বাংলার মনের মাটি ও আকাশে ঘুরে বেড়ানো লক্ষ লক্ষ শহীদের অতৃপ্ত আত্মারা নজরুলের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের জন্য হৈ-হৈ করে উঠল। টাটকা তরুণ যন্ত্রণাগুলির ‘স্মৃতি-শব’ শব্দ হয়ে গান হয়ে মুক্তি পেয়ে যাওয়ার পর, এক এক করে আসতে লাগল বয়স্কেরা— একশ দুশ পাঁচশ হাজার বছরের যন্ত্রণার সামাজিক-মানসিক প্রেতাত্মারা। সবশেষে এসে দাঁড়ালেন মহামায়া, তাঁর শ্যামা রূপের অবগুণ্ঠন খুলে।
হে গায়ক। চেয়ে দেখ। পাঁচ হাজার বছর ধরে আমি পথ হেঁটে এসেছি, কেবল ব্যর্থতা আর অপ্রাপ্তি, অবহেলা লাঞ্ছনা আর ঘৃণা সয়ে-সয়ে আমি উন্মাদ হয়ে গেছি, সর্ব্বস্ব থেকেও বিপর্য্যস্ত ‘এলোকেশী’ হয়েছি, জীবন আমার শুধু ‘নিশিযাপন’। বিশ্বজগতের সকল যন্ত্রণাকে তুমি আপন করে নিয়েছ। আমাকেও এবার তোমার ভিতর-বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দাও। আমি তোমাকে ‘ভুবনমোহিনী’ রূপ দেখাব। তারপর আর সকলের মত আমার গানও বাজিয়ে দাও তোমার দেউড়ীতে। আমি বাইরে থেকে গেলে যে তুমি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সমগ্র জগতের সব বিষপান করে তুমি সম্পূর্ণ নীলকণ্ঠ হয়ে ওঠো। তোমাকে সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য আমি তোমার দুয়ারে এসেছি।
রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব …
… এবং নজরুল তাঁর মনের মণিকোঠার দুয়ার খুলে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেন তাঁর ‘আমি’-রাজার সিংহাসনে। কারণ এ ছাড়া অন্যকোন উপায় নজরুলের ছিল না। প্রশ্ন হল কেন?
বিহার, পুরাণ মতে অঙ্গ দেশ। তান্ত্রিকতায় সে দেশের মানুষের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। নজরুলের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ অঙ্গদেশের সন্তান। সেখান থেকে তাঁরা আসেন আর এক তান্ত্রিক দেশ, বঙ্গদেশ-এর চুরুলিয়ায়। পিতৃহারা নজরুলের শৈশব মুখোমুখি হয়েছিল কঠিন বাস্তবের। ১২টি ভাইবোনের সংসারে তাঁর স্থান মধ্যম ভ্রাতার। অবহেলা পাওয়া দুখু মিঞার বিধিদত্ত বর। গ্রাম্য পরিবেশের সব স্বাভাবিকতার পাশে ইতিহাসের এক ধ্বংসাবশেষ— গড়। পারিবারিক অশান্তি ও দারিদ্র্য তার শিশুমনকে যথারীতি চাবকেছে। মুক্তি পাওয়া গেছে ‘সাকর গোদার’ কাছে, লেটোয়। দশ বছর বয়সে সংসারের জোয়াল কাঁধে, সে জোয়াল ফেলে দিয়ে যাত্রা পালার গান গেয়ে বেড়ানো। রুটি দোকানের ফালতু। মাতালের পাচক। দানের শিক্ষায় বারে বারে করুণার অপমান। স্বাধীনতা আন্দোলনের দীক্ষা। কলঙ্কের তিলকধারণ। সৈনিকের পাঠ। আরব্য সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের সাথে এবং বহুকালক্রমাগত বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির ক্ষীণ ধারার সঙ্গে সমান পরিচয় ও তাতে তৃপ্তিলাভের অভ্যাস।
সৈনিকের পাঠ নিয়ে ফিরে, কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন। পত্রিকাও তখন জীবন সংগ্রাম। ক্রমে শ্রমিক কৃষক ছাত্র আন্দোলনগুলিতে অংশীদার হওয়া। বৈবাহিক জীবনে ঘেরাটোপের সীমালঙ্ঘন। … শৈশব থেকে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত এই কঠোরতার ভিতর দিয়ে হাঁটলেও, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিদিন ঐ কঠোরতার ভিতর থেকে জীবনরসের আহরণ। তাতেই মানসিক তৃপ্তির অভ্যাস। অবশেষে সন্তান হারানোর শোক। এবং সবশেষে কৌলিক গৃহী বরদাচরণ মজুমদারের কাছে পঞ্চ-ম’কার বর্জ্জিত তান্ত্রিক দীক্ষা। অতি সংক্ষেপে এই হল তাঁর জীবনের গতিপথ। … কী আছে এই জীবনধারায়?
জগৎ ও জীবনকে দেখবার জন্য ভারতের নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সবকিছুকে পুরুষ-প্রকৃতির বা শিব-শক্তির যৌথ অস্তিত্ব রূপে দেখা। সমাজ যদি দ্রষ্টব্য বিষয় হয়, তবে শাসক পুরুষ, শাসিত প্রকৃতি। বিদ্যালয় যদি বিষয় হয়, তবে শিক্ষক পুরুষ, ছাত্র প্রকৃতি। এইভাবে জ্ঞান-কর্ম্ম, আত্মা-দেহ, স্বামী-স্ত্রী, জমিদার-প্রজা, মালিক-শ্রমিক, সম্পাদক-লেখক, গায়ক-শ্রোতা, লেখক-পাঠক, সেনাপতি-সেনাগণ, পুরোহিত-ভক্তসম্প্রদায়, ইংরেজ-ভারতীয় … ইত্যাদির দ্বৈততায় বিষয়গুলিকে দেখা। এতে প্রকৃতি সর্ব্বদাই ক্ষমতাহীন এবং পুরুষ ক্ষমতাধর। এবং সর্ব্বদাই পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করছে এবং প্রকৃতি পুরুষের দ্বারা ভুক্ত হচ্ছে। তাই প্রকৃতি নিপীড়িতা, নির্য্যাতিতা, লাঞ্ছিতা ইত্যাদি। (অধুনান্তিক চিন্তাবিদেরা কেউ কেউ এই দৃষ্টিভঙ্গ অর্জ্জন করেছেন এবং তাঁরা এর নাম দিয়েছেন তাঁদের মত করে — ‘কেন্দ্র-প্রান্ত বিরোধের বা পরিপূরকের ধারণা’।৬
এই দৃষ্টিভঙ্গীতে যখন আমরা নজরুলের চলমান জীবন ও সেই জীবনের পাশাপাশি ক্রমবিবর্ত্তনশীল প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাই, আমরা দেখি, নজরুল বেশী ভাগ সময়ই প্রকৃতির ভূ্মিকায় অবতীর্ণ। কিন্তু কেবলমাত্র প্রকৃতির ভূমিকায় অবতীর্ণ থাকলে মানুষ প্রায় কিছুই বুঝতে পারে না। প্রকৃতির ভূমিকাটি কেমন, সেটি তুলনা করার দরকার পড়ে। তাই একবার অন্তত পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। মক্তবের গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেই নজরুলের অনুভবে পুরুষের সুবিধাজনক অবস্থানটি চোখে পড়ে যায়। আর এই শৈশব-সংস্কার তাঁকে তাড়া করে নিয়ে চলে সারাটা জীবন। গায়ক হয়ে, লেখক হয়ে, কবি হয়ে, বক্তা হয়ে, সেই সাধ তিনি পূর্ণ করেন। আবার সমালোচক-লেখক, সম্পাদক-লেখক, বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে, কমাণ্ডার-হাবিলদার সম্বন্ধে তাঁকে প্রকৃতিরূপে বিড়ম্বিত হতে হয়। কিন্তু সব মিলিয়ে তাঁর জীবনে প্রকৃতির অধিকার অধিক। বিপরীতে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ছিল পুরুষের বেশী অধিকার। এই সুবাদে নজরুল ছিলেন ‘পুরুষরূপী প্রকৃতি’, আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ‘প্রকৃতিরূপী পুরুষ’।
এই সেই কারণ, যে জন্য নজরুলের (দুখু মিঞার) ভিতর দিয়ে প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ শুরু হয়। এবং নজরুলও সেই ভূমিকা পালন করে মানসিক অতৃপ্তির জ্বালা থেকে শান্তি পেতে থাকেন। প্রথমে আসে ইংরেজ পুরুষের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রকৃতির কথা, মৌলবাদী ধর্ম্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধর্ম্মপরায়ণ মানুষের কথা, ছাত্রের কথা, শ্রমিকের কথা, কৃষকের কথা, নারীর কথা, পতিতার কথা … ইত্যাদি প্রকৃতির নানা ভূমিকায় লাঞ্ছনার কথা। জীবন মানুষ সমাজ জীবজগৎ জড়জগৎ সকলের দিকে তিনি তাকিয়েছেন প্রকৃতির চোখে, তাদের প্রকৃতি-ভূমিকার স্বাভাবিকতা ও লাঞ্ছনাকে তিনি অনুভব করেছেন। যেখানেই কোনভাবে প্রকৃতি তার হৃত মর্য্যাদা ফিরে পেয়েছে, সেখানেই তিনি আনন্দে উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত।
কিন্তু সব প্রকৃতির চূড়ান্ত যে রূপ, সেই অংরূপিণী পরমাপ্রকৃতিকে যদি তিনি প্রকাশ না করেন, তাঁর সারা জীবনের পথ চলা যে ব্যর্থ হয়ে যায়; অসম্পূর্ণ থেকে যাবেন তিনি। তাই পরমাপ্রকৃতি তাঁর ভুবনমোহিনী রূপ, শ্যামারূপ তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সেকারণে মুসলমান হয়েও তাঁর কিছুই করার ছিল না। তাঁকে তান্ত্রিক দীক্ষা নিতেই হল। গাইতে হল শ্যামাসঙ্গীত। ‘পুরুষ (শিব) রূপী প্রকৃতি’ হিসাবে নজরুল সম্পূর্ণ হয়ে উঠলেন।
প্রশ্ন উঠতে পারে দুটো। প্রথম প্রশ্ন হল, গণসঙ্গীত তো একপ্রকারের শ্যামাসঙ্গীত। নজরুল বহু গণসঙ্গীতের রচয়িতা। তাতেই তাঁর তৃপ্তি হল না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য নজরুলের কালটি অনুভব করা দরকার, এবং আবেগ ও যুক্তির সম্পর্ক জানা দরকার। আবেগের সমুদ্র পেরিয়ে যুক্তি দ্বীপভূমিতে সভ্যতাকে এনে ফেলেছিল শিল্পবিপ্লব। সমুদ্রই দ্বীপভূমির স্রষ্টা। ‘অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছিল’।৭ প্রকৃতি থেকেই পুরুষের জন্ম হয়েছে, জনগণ থেকেই জন্ম হয়েছে তার পরিচালক শ্রেণীর। জীববিজ্ঞান অনুসারেও ‘ফিমেল বডি’ থেকেই ‘মেল অরগান’ রূপে জন্মে ক্রমবিকশিত হতে হতে উচ্চ সোপানের প্রজাতিতে পৌঁছে ‘মেল বডি’ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করেছে। নারীই নরের জন্মদাত্রী। আবেগই একদিন যুক্তির জন্ম দিয়েছে।
প্রাচীন মানুষ আবেগের সমুদ্রে ভাসমান ছিল। সমুদ্রের তলায় যেমন মাটির শক্ত স্তর, আবেগের তলায় তেমনি থাকে যুক্তির কঠিন সমর্থন। দ্বীপভূমির নীচে যেমন পরিস্রুত পাতাল পানীয় থাকে, যুক্তির তলদেশে তেমনি থাকে আবেগের ব্যাকুলতা। পাহাড় পর্ব্বত উপত্যকা নদী নালা বিধৌত জলে সমুদ্রকে নবগুণান্বিত করার জন্যই দ্বীপভূমির জন্ম দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতির পুরুষসৃষ্টির, জনগণের পরিচালক-সৃষ্টির, সমুদ্রে দ্বীপসৃষ্টির, আবেগের যুক্তি-সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ছিল যথাক্রমে প্রকৃতির জনগণের সমুদ্রের আবেগের মানোন্নয়ন। কিন্তু তা না হয়ে ‘পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে’,৮ যা কিনা সমস্ত অহিতের মূল। দ্বীপ আজ সমুদ্রশাসনে ব্যস্ত। যুক্তি আজ আবেগের গলা চেপে ধরেছে।
যুক্তি নিজেই পুরুষ, আবেগ স্বয়ং প্রকৃতি। আবেগ জন্ম দিয়েছিল শ্যামাসঙ্গীতের। এটি ছিল কর্ম্মী-জনতার সংগ্রামের বঙ্গীয় প্রাগাধুনিক ডিসকোর্স। যুক্তি জন্ম দিল গণসঙ্গীতের। এটি ছিল কর্ম্মী-জনতার সংগ্রামের ইউরোপীয় আধুনিক ডিসকোর্স। কাঁটা চামচে টেবিল চেয়ারে বসে খেয়ে বাঙালীর মন ভরে না, তার পাত পেড়ে আসনে বসে যাওয়া চাই। নজরুল এই দ্বিঘাত সময়ের মানুষ। তাঁকে দুটোই গাইতে হয়েছিল। তবে বাঙালী বলে, পুরুষরূপী প্রকৃতি বলে, নজরুলের যেমন শ্যামাসঙ্গীতেই বেশী শান্তি, তাঁর শ্রোতাদেরও শ্যামাসঙ্গীতেই তৃপ্তি হয়েছিল। শ্যামাসঙ্গীতকার নজরুল অনাদিকালের তান্ত্রিক ধারাবাহিকতার শেষ উপনদী।
দ্বিতীয় প্রশ্ন : ‘তান্ত্রিকতার যা ছিরি’ বর্ত্তমানে দেখা যায় তা কি গ্রহণযোগ্য? উত্তর হল, ফলিত প্রয়োগ হওয়ার কালে যে কোন ধারণার, বৈপ্লবিক চিন্তার, তত্ত্বের, দুই রকম বিচ্যুতি হয়, হওয়া স্বাভাবিক। একদিকে মৌলবাদ তত্ত্বটিকে গ্রাস করে, তার পত্রপুষ্প ছিঁড়ে ফেলে, তাকে নখদন্তহীন জরদ্গব বানিয়ে ফেলে ও ক্ষমতার সহায়ক করে তোলে। ‘একদিন যে গতির পক্ষে বীরত্ব দেখিয়েছিল’, তাকে সে ‘স্থিতির পক্ষে বীর বলে ঘোষণা করে’।৯ বেদজীবী মৌলবাদী পুরোহিততন্ত্র তান্ত্রিকতাকে গ্রাস করে ফেলে অনেকাংশেই। বিপরীতে নৈরাজ্যবাদের মতই তান্ত্রিকতার বিকার ঘটে নানারকম সঙ্কীর্ণ নোংরামীতে। দু-দিকের বিচ্যুতি বাদ দিয়ে যাকে পাওয়া যায়, কথা হচ্ছে তাকে নিয়ে। তার গৌরব চির-অম্লান।
কালো মেয়ের আঁধার কোলে শিশু রবি শশী দোলে …
ব্যক্তিগত বিপর্য্যয় থেকে যেমন মানুষের জ্ঞানোদয় হয়, তেমনি সামাজিক বিপর্য্যয় থেকে জ্ঞানোদয় হয় সমাজের; সমাজ এককালীন একরাশ গ্রন্থ প্রসব করে। রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড ওডিসি এসবই সামাজিক বিপর্য্যয়ের ফসল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালেও আমরা এই প্রকার সামাজিক জ্ঞানোদয় হতে দেখেছি। প্রতিষ্ঠিত বৈদিক সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রথম যে মহাবিদ্রোহ তারই ফসল ছিল উপনিষদ গ্রন্থাবলী। বহু যুগ অতিক্রান্ত হবার পর, আমরা তার উত্তরাধিকার পাই রবীন্দ্রনাথে। কেন?
পুরাণ অনুসারে পুরুষ দুই প্রকার— শিব ও দক্ষ। প্রকৃতিপ্রেমিক পুরুষ ও প্রকৃতিভোগী পুরুষ। শিব ‘পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার’-এর নীতিতে বিশ্বাসী। দক্ষ ‘পুরুষ প্রকৃতির ভোক্তৃ-ভোগ্যা সম্পর্কে’ বিশ্বাসী। দক্ষ বৈদিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা, শিব ঘোর বেদবিরোধী। ভারতের মাটিতে এই দুই প্রকার পুরুষের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বর্ত্তমান। রবীন্দ্রনাথ যখন নিজেকে ‘প্রকৃতিরূপী পুরুষ’ রূপে সপ্রমাণ করতে গেলেন, তাঁর উপর শিবের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার উত্তরাধিকারের দায় চাপল। উপনিষদের বাণী— ‘তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা, অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে’– তাঁর ভিতর দিয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠতে চাইল। তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত গেয়ে উঠলেন।
মহাকাল এমনি করেই ভাবায়, করায়। যথার্থ পুরুষ, যে কিনা বৈদিক যুগের সূত্রপাতেই ক্ষমতাচ্যুত (দ্রষ্টব্য– শিবহীন যজ্ঞ), তাঁর (শিবের) সেই উত্তরাধিকার যুগ যুগ বাহিত হয়ে এসে ঠেকল প্রকৃতিপ্রেমিক, ‘প্রকৃতিরূপী পুরুষ’ রবীন্দ্রনাথে। তিনি উপনিষদের বাণীকেই বিশদ করলেন, গাইলেন ব্রহ্মসঙ্গীত। অপরদিকে প্রকৃতির (শক্তির) উত্তরাধিকার বহুযুগ বাহিত হয়ে এসে উপনীত হল পুরুষপ্রেমিক, ‘পুরুষরূপী প্রকৃতি’ নজরুলে। তিনি প্রকৃতির (জনগণের) লাঞ্ছনাকে প্রতিবাদে মূর্ত্ত করে তুললেন— গেয়ে উঠলেন শ্যামাসঙ্গীত। এমনিই হয়। ‘পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার’-এর এইরূপ পরিপূরক ভাবাদর্শের প্রণোদনাই স্বাভাবিক ও যথার্থ ছিল; হলও তাই। এভাবেই তাঁরা দুজনেই সম্পূর্ণ হয়ে উঠলেন। দুই মহামানবের ভিতর দিয়ে ইতিহাস তার উদ্দেশ্য এভাবেই সিদ্ধ করল। ভারত ইতিহাসের শিব-শক্তির দুই আদি ধারা বহু যুগ ধরে বহু মানুষের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে এসে অবশেষে রবি ও নজরুল রূপে বঙ্গমানসের আকাশে প্রতিভাত হয়ে গেল।
তাঁরা কি একথা জানতেন না? তাঁদের রচনায় তাঁদের এই ভূমিকার কথা নেই কেন? উপনিষদ যখন রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে, তিনি কি জানতেন না, তিনি কী করছেন? কিংবা তন্ত্রসাধক নজরুল কি তাঁর ভূমিকার কথা বুঝতে পারেননি? বস্তুত তাঁরা যে যার ভাবাদর্শ বিষয়ে অবশ্যই সচেতন ছিলেন এবং কাজ করছিলেন তাঁদের আপাত উপলব্ধি ও আপাত সচেতনতা দিয়ে। কিন্তু ইতিহাস তাঁদেরকে দিয়ে কী করিয়ে নিচ্ছে, তা জানার উপায় তাঁদের ছিল না; কারোরই থাকে না। কারণ— ‘ভাবাদর্শ এমন একটি প্রক্রিয়া যা তথাকথিত মনীষী যে সচেতনভাবে সম্পাদন করেন, সেকথা ঠিক। কিন্তু ঐ সচেতনতা ভ্রান্ত সচেতনতা; তাঁকে চালিত করে যে প্রকৃতি প্রেরণাশক্তি, তা তাঁর কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। অন্যথায় তা ভাবাদর্শগত প্রক্রিয়াই হয়ে উঠত না।’ (এঙ্গেলস)।
তবে কেন ভারতাত্মার এই দুই প্রতিনিধিকে শুধুমাত্র রোমাণ্টিক কবি ও বিদ্রোহী কবি বলে চালানো হয়? কেবলমাত্র লেখনী নিয়ে দুজনের কেউই তো বসে থাকেননি। উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে তাঁরা যে যেভাবে পারেন ঢুকে পড়েছেন। কর্ম্মজীবন তাঁদের অজস্র ঘটনাবলীতে মুখর। মুখর তাঁদের লেখনীও, নানা দিকে, নানা ধারায়, নানান বিষয়ে। সেই সমগ্র-রবীন্দ্রনাথ ও সমগ্র-নজরুলকে কেন ছেঁটে ফেলে সঙ্কুচিত করা হয় শুধুমাত্র রোমাণ্টিক কবি ও বিদ্রোহী কবিতে?
নজরুল ক্ষমতাবিরোধী, কর্ম্মী জনগণের সমর্থক, প্রচলিত ব্যবস্থার সমালোচক, গ্রাম্য, আবেগতাড়িত ও বিবেকতাড়িত, চারণ কবি, মোল্লাতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের বিরোধী। রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির বিরোধী যে লোকসংস্কৃতি তার তিনি ধারক বাহক ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায় তিনি বহুরৈখিক মানুষ। দেখা হয়, এর কোন রেখাটি ক্ষমতার প্রয়োজনের সঙ্গে মেলে। ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে গড়ে ওঠা নতুন ক্ষমতাকেন্দ্রের কাছে সমগ্র নজরুল বড়ই অস্বস্তিকর। কেবল ‘কমন’ পাওয়া যায় তাঁর অবিসংবাদিত ব্রিটিশ-বিরোধিতা। ঐ একটি বিন্দুতে এ যুগের ক্ষমতা নজরুলকে দলে পায়। সেই তকমাটি নজরুলের কপালে সাঁটিয়ে সে দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নেয়।
প্রথমত, এর ফলে, ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে নজরুলের বিদ্রোহী গণসঙ্গীত ও কবিতাগুলির ব্যবহার ও তার গণপ্রীতিকে ব্যবহার অনায়াসসাধ্য হয়ে যায়। নব্য ক্ষমতা এইভাবে জনগণের সমর্থনকে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করে। ভারত স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর ঐ বিদ্রোহী গানগুলির আর প্রয়োজন থাকে না। চীন ভারত যুদ্ধকালে আবেগ উদ্দীপনার আকাল পড়লে পুনরায় বিদ্রোহী কবির ঐ রচনাগুলিকে ডেস্কের তলা থেকে খুঁজে বের করে ধুলো ঝেড়ে ব্যবহার করা হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ও কখনও কখনও ক্ষমতা নজরুলের খোঁজ করে। এভাবেই অসুরসমাজ নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কখনও কখনও শক্তির আরাধনা করত।
দ্বিতীয়ত ‘বিদ্রোহী’ কবির তকমাটি প্রয়োগ করে নজরুলের বাকি সমস্ত গুণাবলীকে ক্ষমতা চাপা দিতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ, ক্ষমতার পক্ষে অস্বস্তিকর যে ‘সমগ্র নজরুল’, তাকে ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ‘বিদ্রোহী কবি’ তকমাটিকে। যেমন ‘কবিগুরু’ রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করা হয়েছে দার্শনিক সমাজতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে ফেলতে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল বহুরৈখিক শিবশক্তির যথার্থ উত্তরাধিকারী বলেই ক্ষমতার পক্ষে বড়ই অস্বস্তিকর। তাদের পত্রপুষ্প ছিঁড়ে ফেলে নখদন্তহীন করে ক্ষমতা তাদের ব্যবহার করে থাকে। নজরুলের এই দুরবস্থা দেখে বাংলাদেশ তাকে দত্তক নিয়ে নেয়, কিন্তু এই আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশ সরকার কতখানি স্বস্তিতে আছে বলা মুশকিল। তবে রবীন্দ্রনাথের জন্য এখনও কোন খদ্দের পাওয়া যায়নি।
এই ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করেন কারা? নজরুল সমালোচকদের বিশাল তালিকা। কে নেই সেখানে? গোটা এলিট সমাজটাই সেখানে থাবা গেড়ে বসে আছেন। অতিদক্ষিণ থেকে অতিবাম পর্য্যন্ত সব্বাই। তাঁদের কত অভিযোগ অনুযোগ নজরুলের বিরুদ্ধে। আসলে, সেই সোচ্চার ও গুপ্ত নজরুল-বিরোধিতার পিছনে যে প্রক্রিয়া, সে প্রক্রিয়া খুবই দীর্ঘ। তবে সে ভিন্ন প্রসঙ্গ।
কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন …
তন্ত্রসাধনা (study of systems and its practices) করতে গিয়ে ভারতসমাজ বস্তুদেহ (Physics), মানবদেহ (Physiology), সমাজদেহ (Sociology) থেকে ব্রহ্মাণ্ডদেহ (Cosmology) পর্য্যন্ত সকল প্রকার ‘দেহতত্ত্ব’-এর যে বহুরৈখিক সাধনা করেছিল, তা বিস্ময়কর। দেহমাত্রেই আদিতে অদ্বৈত ব্রহ্ম। বিন্দুরূপিনী বাণলিঙ্গ বুড়াশিব পরমাপ্রকৃতি ইত্যাদি তার নানা নাম। শিব শক্তির এক অভেদাত্মক অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ হল এই পরমাপ্রকৃতি। সমাজদেহের দিক থেকে এর আর এক নাম একার্ণব (সাম্যবাদী সমাজ)। ভারতীয় দর্শন অনুসারে ‘একার্ণব-সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-একার্ণব’ এই হল জগতের বিকাশের ক্রমবৃদ্ধিশীল চক্রাকার গতিপথ। এক একার্ণব থেকে ক্রমশ বৃহত্তর একার্ণবে উত্তীর্ণ হতে থাকা। আর, এভাবে সব কিছুই যে ‘একাকারের দিকে এগুচ্ছে কোন না কোনভাবে’১০ সেকথা অনেকেই জানেন।
রবীন্দ্রনাথ ঐ একের নাম দিয়েছিলেন ‘অরূপরতন’। প্রকৃতি-ভোগী বিকৃত ‘পুরুষ’কে তিনি চিহ্ণিত করেছিলেন ‘অচলায়তন’ নামে। কখনও বা তিনি তার নাম দিয়েছেন ‘স্থবিরপত্তনের রাজা মন্থর গুপ্ত’। বিপরীতে নজরুল ঐ একে পৌঁছেছিলেন বিশ্বমায়ের ‘শ্যামা’-রূপে। রবীন্দ্রনাথ পুরুষের দিক থেকে এগিয়ে ঐ অদ্বৈতে উন্নীত হয়েছেন; নজরুল প্রকৃতির দিক দিয়ে এগিয়ে সেই অদ্বৈতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুজনেই ‘স্থবিরপত্তনের রাজা’র বা মৌলবাদের (দক্ষের) ঘোর বিরোধী। দুজনেই পৌঁছেছেন একই অর্দ্ধনারীশ্বরে, দুদিক থেকে। তাই বস্তুত শিবশক্তির অভেদাত্মক নীতি অনুসারে তাঁদের মধ্যে ভেদ নেই, তাঁরা পরস্পরের পরিপূরক, এক এবং অভিন্ন, বিশ্বমানবের দুই রূপ মাত্র। বাস্তবে তাঁদের দুজনের কানে পরস্পরের বিরুদ্ধে বহু বিষ ঢালা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নজরুল-প্রেমে এবং নজরুলের রবীন্দ্র-ভক্তিতে ঘাটতি দেখা যায়নি।
সভ্যতার শৈশবের নেতৃত্বে থাকার সুবাদে, মহান ঐতিহ্যের হকদার হওয়ার কারণে বহুরৈখিক চিন্তাপদ্ধতি ভারতের সহজাত। উত্তম অধিকারীর সামাজিক মর্য্যাদা ভূলুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, নিম্ন-অধিকারীর সামাজিক মর্য্যাদা চূড়ান্ত হওয়া সত্ত্বেও, এবং পাশ্চাত্যের প্রতীকী (রূঢ়ি) ভাষা ও চিন্তার নিদারুণ চাপ থাকা সত্ত্বেও সেই উত্তরাধিকার যে আমাদের আজও আছে, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে দেখে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। এই বহুরৈখিক চিন্তাপদ্ধতি একপ্রকার ‘জ্ঞানের সমীকরণ’ সেরে ফেলে নিজের অজান্তেই।
আজকের পদার্থবিজ্ঞান ‘গতির-সমীকরণ’ থেকে সবেমাত্র ‘জ্ঞানের সমীকরণ’-এ পা রেখেছে। এখনও বহুরৈখিক চিন্তাপদ্ধতি তাঁরা রপ্ত করে উঠতে পারেননি। তাঁরা দেহতত্ত্বের সাধনা করছেন পৃথক পৃথক ভাবে— Physics (বস্তুদেহ), Chemistry (রসদেহ), Biology (জীবদেহ), Physiology (মানবদেহ), Sociology (সমাজদেহ), Cosmology (ব্রহ্মাণ্ডদেহ) এসব তাঁদের দেহতত্ত্বের পৃথক পৃথক সাধনা। যেন যে-যার মত নিজের জায়গা থেকে পৃথক সিঁড়ি আর সরঞ্জাম নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে এভারেষ্টের চূড়ায় উঠতে পেরেছেন। কিন্তু সাধনা করলে তো সিদ্ধিলাভ হবেই।
রবীন্দ্রনাথ ‘প্রকৃতিরূপী-পুরুষ’ হয়ে তার আরাধনা করলেন, পরমাপ্রকৃতি তাঁর কাছে ধরা দিল ‘অরূপরতন’ (পুং) রূপে। নজরুল ‘পুরুষরূপী-প্রকৃতি’ হয়ে তাঁর সাধনা করলেন, পরমাপ্রকৃতি তাঁর কাছে ধরা দিল ‘শ্যামা-মহামায়া’ (স্ত্রী) রূপে। আদতে ঐ ব্রহ্ম পুরুষ বটে, প্রকৃতিও বটে, সম্ভাবনা ৫০:৫০। পদার্থবিজ্ঞানীরা সেই ‘অনিশ্চয়তাতত্ত্বে’ উপনীত হয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ধরা দেওয়ার আগে সূক্ষ্মতম তেজস্ক্রিয় পরমাণু কণা পুরুষ (আপ-স্পিন) না প্রকৃতি (ডাউন-স্পিন) তা অনিশ্চিত। ধরতে গেলে পাওয়া যায় যে কোন এক রূপে। মানবদেহ-বিজ্ঞানীরা DNA-RNA-এর পুরুষ-প্রকৃতির দ্বৈততা পেরিয়ে অদ্বৈত জিনতত্ত্বে পৌঁছানোর নেশায় মত্ত। সমাজবিজ্ঞানীরা ‘নলেজ-ওয়ার্কার’ (পুরুষ) ও ‘সার্ভিস-ওয়ার্কার’ (প্রকৃতি) বিভাজনটিতে উপনীত হয়ে গেছেন।
এমন সমাজের মডেল এখনও প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, যেখানে পরিচালক ও পরিচালিতকে আলাদাভাবে চেনা যায় না, সবাই পরিচালক (পুরুষ), সবাই পরিচালিত (প্রকৃতি)। সেই একার্ণবে এখনও তাঁরা পৌঁছতে পারেননি, যেখানে যে কোন মানুষই পুরুষও হতে পারে, প্রকৃতিও হতে পারে, সম্ভাবনা ৫০:৫০। তবে মহাকালের অস্পষ্টতাকে ঐ সকল পোস্টমডার্ণ সুচিন্তকেরা ‘রদবদলের ধারণা’য় বিন্যস্ত করে ফেলেছেন প্রায়। ‘ইকোফেমিনিষ্ট’ দার্শনিকেরাও খুঁজে বেড়াচ্ছেন এক অর্দ্ধনারীশ্বরকে, তাঁরা সেই কাঙ্ক্ষিত মডেলটির নাম দিয়েছেন— Androgyny।
সাহিত্যিকরাও এর কাছাকাছি পৌঁছে বলতে শুরু করেছেন, সাহিত্য হল ‘The idea of a work having two senses’; এ হল ‘indefinable’-কে define করার চেষ্টা মাত্র। ব্যাপারটি নীৎশের নিকট ধরা দিয়েছিল মহামিথ্যা (মহামায়া) রূপে— ‘Artistic pleasure is the greatest kind of pleasure, because it speaks the truth quite generally in the form of lies’ … জ্ঞানজগতের প্রায় সকল শাখাতে, সকল উপশাখাতে, সর্ব্বত্র চলেছে এই অগ্রগতি। সবাই চলেছে পুরুষ প্রকৃতিকে ধরতে, সেখান থেকে যাতে পরমাপ্রকৃতিকে একদিন ধরে ফেলা যায়। আর শেষমেষ সেই চূড়ান্তে উত্তীর্ণ হওয়া গেছে কি না, তা বুঝতে হবে পূর্ব্বদিগন্তের দিকে তাকিয়ে। সেখানে পৌঁছে দেখা যাবে, সেখানে ইতোমধ্যেই পতাকা পুঁতে বসে আছেন — রবীন্দ্রনাথ নজরুল।
মালটিন্যাশনালের নেতৃত্বে চালিত এই বিশ্বসমাজে এখন প্রকৃতিই ভরসা। ভারতের মত হীন দেশগুলিই সরবরাহ করছে জ্ঞান কর্ম্মের জগতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পৌরুষ। একজিকিউটিভের প্রধান সরবরাহকারী এখন তৃতীয় বিশ্ব। চিন্তার, তত্ত্ব-তালাশের, প্রাণের, বিকাশের পক্ষে যা কিছু সদর্থক, সেগুলি পাওয়া যাচ্ছে ‘কালো মেয়ের পায়ের তলায়’। কৃষ্ণা লোধ যখন কলম ফসকে লিখে ফেলেন, ‘শহরের আর কিছু এখন দেবার নেই, এবার দেবে গ্রাম’; ১১ ইতিহাস তার কলম দিয়ে এই সত্যি কথাই লিখিয়ে নিয়েছিল যে, প্রকৃতির মর্য্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা আসন্ন; কেননা আলোর নাচন এখন সেখানেই।
টীকা :
১. মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সঙ্কলন থেকে।
২. এই বাক্যাংশগুলি বায়ুপুরাণ থেকে গৃহীত।
৩. ‘শ্রম’ শব্দের প্রতিশব্দ ‘তপস্যা’ (দ্র. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’। সুতরাং প্রাচীন ভাষায় ‘শ্রমিক’ বলতে ‘তপস্বী’ বোঝায়। তপ-স্ব বা আপন শ্রমের মালিক। এই তপ (শ্রম) যেখানে প্রয়োগ হত, সেই জমিগুলিকে বলা হত ‘তপশীলভুক্ত’। আজও বলা হয়।
৪. সাধনপ্রদীপ। – স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী।
৫. ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে উৎসব শব্দের অর্থ – ‘উৎস বহন করে যে’। আদি বৈপ্লবিক ঘটনাটিই উৎস। তারই স্মৃতি ‘বহন’ করতে থাকে উৎসব। বিশেষ বিশেষ উৎসব সেই সেই বিশেষ আদি ঘটনার স্মৃতিবাহক।
৬. এই পুরুষ-প্রকৃতি বিষয়ক ভারতীয় ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে ‘পরমাপ্রকৃতিতত্ত্ব : গ্র্যান্ড ইকোফেমিনিজম’ নিবন্ধে।
৭. এটি ঋগ্বেদের একটি শ্লোকাংশ। দশম মণ্ডল। ১৭শ সুক্ত।
৮. কপিলের ‘সাংখ্য’।
৯. রবীন্দ্রনাথের ‘কালান্তর’।
১০. কথাটি শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন ১৩০৩ বঙ্গাব্দের নববর্ষের রচনায়, আনন্দবাজার পত্রিকায়।
১১. আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীমতী কৃষ্ণা লোধের একটি নিবন্ধ থেকে।
(নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ‘নজরুল ফাউণ্ডেশন পত্রিকা’র জানুয়ারী ১৯৯৭ সংখ্যায়। পরে ‘দিশা থেকে বিদিশায়…’ গ্রন্থে তা খানিক পরিমার্জ্জিত হয়ে চারবাকে পুনঃপ্রকাশ করা হল।
— সম্পাদকীয়।)
কলিম খান
জন্ম: ০১ জানুয়ারী ১৯৫০ মামুদাবাদ (মেদিনীপুর)। মৃত্যু: ১১ জুন ২০১৮ কলিকেতা।কলিম খানের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী:
১. মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে (১৯৯৫)
২. দিশা থেকে বিদিশায় : নতুন সহস্রাব্দের প্রবেশবার্তা (১৯৯৯)
৩. জ্যোতি থেকে মমতায় : ফ্রম এনলাইটেনমেন্ট টু…. (২০০০)
৪. পরমাভাষার সংকেত (২০০১)
৫. আত্নহত্যা থেকে গণহত্যা : আসমানদারী করতে দেব কাকে (২০০২)
৬. পরমা ভাষার বোধন উদ্বোধন : ভাষাবিজ্ঞানের ক্রিয়াভিত্তিক রি-ইঞ্জিনিয়ারিং (২০০২)কলিম খান ও রবি চক্রবর্ত্তীর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী:
১. বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ (২০০৬)
২. অবিকল্পসন্ধান : বাংলা থেকে বিশ্বে (২০০৮)
৩. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ, ১ম খণ্ড (২০০৯) ও বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ, ২য় খণ্ড (২০১১)
৪. সুন্দর হে সুন্দর (২০১১)
৫. বঙ্গযান (২০১২)
৬. সরল শব্দার্থকোষ (২০১৩)
৭. বাংলা বাঁচলে সভ্যতা বাঁচবে (২০১৩)
৮. বঙ্গতীর্থে মুক্তিস্নান : বাংলাভাষা থেকে সভ্যতার ভবিতব্যে (২০১৫)
৯. ভাষাই পরম আলো (২০১৭)