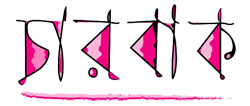‘শাস্ত্র’ শব্দের অর্থ ‘শাসনসাধন’, অর্থাৎ যার দ্বারা শাসন করবার কাজটি সাধন করা যায়, অর্থাৎ কিনা ‘শাস্ত্র’ মানে শাসনের হাতিয়ার। ভারতীয় কোষকারগণ জানাচ্ছেন যে, শব্দের এইপ্রকার অর্থ কারও স্বকপোলকল্পিত নয়, শব্দটির ভিতরেই তা পাওয়া যায়। যে সকল বর্ণকে নিয়ে শব্দটি গড়ে ওঠেছে, তারাই ঐরূপ অর্থ ধারণ করে রেখেছে। শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকে সে কথা আমরা জানতে পারি। কোষকারগণ তাই শব্দের অর্থ প্রদান কালে প্রথমেই ব্যুৎপত্তি উল্লেখ করে থাকেন। এক্ষেত্রে যেমন ‘শাস+ত্র(ষ্ট্রণ্)ণ শব্দ থেকে অর্থ নিষ্কাশনের এই বিধি অতি প্রাচীন এবং ভারত যখন এই বিধি প্রয়োগ করতে শুরু করেছিল ইউরোপ তখনও নোম্যাড রেস্ (Nomad)। সংস্কৃতের যোগ্য সন্তান হওয়ার সুবাদে কৃত্তিবাস কাশীরামের প্রাচীন বাঙলা ভাষাও এই বিধি দ্বারাই শাসিত ছিল। তা শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ গ্রন্থে যথারীতি প্রথমে ‘শাস্ত্র’ শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে, তারপর ‘শাসনসাধন’ অর্থটি সরবরাহ করেছেন। ব্যুৎপত্তির গোড়ায় থাকে একটি ক্রিয়া, এক্ষেত্রে যেমন ‘শাস্’ ক্রিয়াটি, তারই ওপর ভিত্তি করে তিনি ঐরূপ অর্থ প্রদান করায় একে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থ বলা যায়। ঐরূপ অর্থ নিষ্কাশন যে নতুন নয়, পূর্ব্বসূরীরাও এইরকমই করে গেছেন, তা দেখানোর জন্য অতঃপর তিনি পূর্ব্বসূরীদের মধ্যে ‘অমরকোষ’-এর উল্লেখ করেছেন; উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ নিষ্কাশন বিধি যেখানে সম্পূর্ণ মান্য করা হয়েছে।
অবশ্য ইংরেজী গ্রীক জার্ম্মানী ইত্যাদি কোন ভাষাই এরূপ ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির দ্বারা শাসিত নয়। আধুনিক ভাষাজগতে কনভেনশনাল, অ্যাকসিডেণ্টাল বা প্রতীকী শব্দার্থবিধি মান্য করা হয়। তাতে যে কোনও শব্দের অর্থ প্রথমবার কারও নিকট থেকে জেনে নিয়ে, তারপর সেই অর্থ স্মরণে রাখতে হয়। শব্দের ভিতরে মাথা কুটলেও সেখান থেকে সরাসরি কোনও অর্থ নিষ্কাশন করা যায় না। আধুনিক বাঙলা সহ বিশ্বের প্রায় সমস্ত ভাষাই এই প্রতীকী শব্দার্থবিধি মান্য করে থাকে। কিন্তু প্রাচীন বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে এই বিধি খাটে না। তাই বাঙলা ভাষার বিশেষত্ব এই যে, সে দৃশ্যত একরম হলেও দুইরকম শব্দার্থবিধির দ্বারা শাসিত।
ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির দ্বারা শাসিত হলে, শব্দের ভিতর থেকেই তার বহুরৈখিক অর্থ বেরিয়ে আসে। এক্ষেত্রে যেমন, যার দ্বারাই শাসন ক্রিয়াটি সাধন করা যাবে তাকেই বলা হবে ‘শাস্ত্র’। অর্থাৎ কিনা শাস্ত্র কোনও নির্দ্দিষ্ট বস্তু নয়, উক্ত ক্রিয়াটি যেই সাধন করে সেই শাস্ত্র! সেটি একটি বই না লাঠি তা বিচার্য্য নয়। যাথাতথ্য নয়, যাথাতত্ত্বের ওপর এই বিধির নিষ্পলক দৃষ্টি। তাই যুগে যুগে ‘শাস্ত্র’ শব্দের উদ্দিষ্ট বদলে গেছে, শব্দার্থও বহুরৈখিকতা থেকে ক্রমান্বয়ে একরৈখিকতায় অধঃপতিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন— শ্রীধর স্বামীর মতে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি, মেদিনীকোষ মতে আগম এবং অন্য একমতে সাংখ্য যোগ তর্কপূর্ব্বোত্তরমীমাংসা সূত্র স্মৃতি কামন্দকাদি নীতিগ্রন্থগুলি ‘শাস্ত্র’ পদবাচ্য; অর্থাৎ ঐগুলির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কালে শাসন করবার কাজটি সাধন করা যেত। এই নিরিখে পুরাণ কোরাণ সংবিধান সব গ্রন্থই শাস্ত্র পদবাচ্য সন্দেহ নেই।
শাসনের হাতিয়ার জিনিসটা, ব্যবহৃত হবার আগে, কমপক্ষে দুটি পূর্ব্বশর্ত্ত দাবী করে। তার চাই শাসক ও শাসিত, অর্থাৎ ঐ হাতিয়ার যিনি প্রয়োগ করবেন তাঁকে এবং যাঁর ওপর তা প্রযুক্ত হবে তাঁকে। আপনার আত্মশক্তি যদি বলবান হয়, আর সে যদি আপনার প্রবৃত্তির স্বভাববিরোধী হয়; অর্থাৎ আপনার অসংখ্য দেহকোষের দাবীগুলিকে শাসন করতে চায়, সে ক্ষেত্রে আপনি শাস্ত্রের প্রয়োগ করতে পারেন। আবার কোনও সমাজদেহের আত্মশক্তি (জাতীয়তাবোধ ও তার মোড়লগণ যদি বলবান হয় এবং সে যদি অসংখ্য সমাজ দেহকোষের (জনসাধারণের) দাবীগুলিকে শাসন করতে চায়, সে ক্ষেত্রেও শাস্ত্রের প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাহলে দেখা যাছে, দৃষ্টিভঙ্গীটাই একরৈখিক নয়, বহুরৈখিক। মানবদেহ হোক আর সমাজদেহই হোক, তাদের শাসন করার ব্যাপার শাস্ত্রের প্রয়োগ প্রশস্ত। এক শাস্ত্রের সাহায্যে সকল দেহই শাসন করা যায়। যায় বলেই, ভারতবর্ষ বহু প্রাচীনকাল থেকে এক ঢিলে দুই পাখী মেরে আসছে।
ইউরোপ এই জিনিসের সঙ্গে পরিচিত নয়। যাথাতথ্য তাদেরকে যতখানি গর্ব্বিত করেছে, ততখানি ধীমান করেনি। তাই মানবদেহ ও সমাজদেহকে এক সঙ্গে দেখবার কৌশল তাদের অজানা। সেই কারণে সমাজদেহকে শাসন করবার ব্যাপারে তারা প্রধানত অস্ত্রের ওপরই নির্ভরশীল। আমাদের ‘অস্ত্র’-এর পাশাপাশি ছিল ‘শস্ত্র’, যার যথার্থ প্রতিশব্দ পর্য্যন্ত তাদের ভাষায় নেই, আর ‘অস্ত্রশস্ত্র’ আমাদের এমন উত্তরাধিকার যে আমরা কথায় কথায় শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। ‘শস্ত্র’বিদ্যা আমাদের অধ্যয়নেরও বিষয় এবং তা বহু প্রাচীনকাল থেকেই। আর সেই সকল শস্ত্রের আধার বলেই উল্লিখিত গ্রন্থগুলিকে ‘শাস্ত্র’ বলা হয়ে থাকে। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরকেন্দ্রিক সভ্যতার আদি আই-সি-এস প্রশাসকগণ ঐ গ্রন্থগুলির ওপর নির্ভর করে যে শাসন চালাতেন, তা জনসাধারণের দেহের চেয়ে তাদের মনের ওপর অনেক বেশী কড়া হয়ে এঁটে বসত, কাজটা হত পাকা। অস্ত্রের শাসনে যদি পাকা করা হত, তাহলে তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাকত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনোই থামত না(১), যা ইউরোপের বৈশিষ্ট্য। আধুনিক ভারতে দেরাদুনে আমাদের হবু সিভিল সার্ভেণ্টগণ যে সকল গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে ভারতের জনসাধারণকে শাসন করবার কৌশল রপ্ত করেন, সেগুলিই এযুগের শাস্ত্র বা শাসনের হাতিয়ার। সেখান থেকে শস্ত্র চালনার কায়দা-কসরত শিখে, তদনুযায়ী তাঁরা তাঁদের কলম চালান; কেমন চালান সেকথা আমরা সবাই জানি; আর কে না জানে কলম তরবারির চেয়ে বেশী শক্তিশালী? ভারত একটা প্রাচীন দেশ, অসংখ্য মৌলিক আবিষ্কারগুলির পাশাপাশি, কলম দিয়ে নিঃশব্দে খুন করবার বিদ্যাও সে আবিষ্কার করেছিল বহু প্রাচীনকালে এবং সেই বিদ্যাও হয়েছিল শাস্ত্র পদবাচ্য। আর ঐরূপ শাসনের হাতিয়ার বলেই জনসাধারণ ওগুলিকে কখনও সৎ-শাস্ত্র বলেনি। ‘সচ্ছাত্র’ বলেছে ‘শ্রুতিস্মৃতিবিরোধী শাস্ত্র’(২)-কে। সেই সচ্ছাত্রের ‘দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি’(৩) [ = to the people and from the people(৪) = দিবে আর নিবে ] নির্দ্দেশ যদি মান্য করি, তবে একথা বলতেই হয় যে, জনসাধারণের মতে বেদবিরোধী শাস্ত্রই যে সৎ শাস্ত্র হয়, এতদিন সেকথা আমরা খেয়াল করিনি।
বস্তুত আদিম সাম্যবাদী সমাজের হাত ধরে যে বহুরৈখিক প্রাচীন সংস্কৃতের উদ্ভব, পণ্যবাহী সমাজের হাত ধরে সে ক্রমান্বয়ে এগোচ্ছিল একরৈখিক আধুনিক বাঙলা ভাষার দিকে। আর সেই সময়, একদিন ব্রিটিশের আগমন ঘটে ও বাঙালীর ভাষার ভিতরেও সে উপনিবেশ স্থাপন করে, যার অনিবার্য্য ফলশ্রুতি ঘটে বাঙলা ভাষার আত্মাবদলে। সেইজন্যেই কেরী সাহেব থেকে সুনীতি চাটুজ্জে সাহেব পর্য্যন্ত ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সাহেবদের কাছ থেকে আমরা যখন বাঙলা ভাষাটা নতুন করে শিখলাম, ততক্ষণে সেই অফিসিয়াল সাহেবী বাঙলার আত্মা বদলে গেছে এবং শরীরেও হাত পড়েছে, প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষার মত বাঙলা ভাষার ভিতর থেকেও ভারত-আত্মার বিদায় পর্ব্ব সমাধা হয়েছে এবং ইউরোপীয় আত্মার অনুপ্রবেশ ও অধিষ্ঠান সাঙ্গ হয়েছে। অর্থাৎ কিনা, ইউরোপ কেবল ভারতেই উপনিবেশ স্থাপন করেনি, ভারতীয়ের জীবনের সর্ব্বত্র, তার ভাষায় আচারে ব্যবহারে জীবিকায় মনে শিল্পে সাহিত্যে এককথায় সমগ্র জীবনযাত্রায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।
বাঙলা ভাষার দেহে ইউরোপীয় আত্মা ঢুকে পড়ার পর বাঙলা শব্দাবলীর ভিতর তাদের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থগুলিকে অর্থাৎ ভারতাত্মাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই ‘শাস্ত্র’-এর ভিতর ‘শাসনসাধন’কেও পাওয়া যায়নি; পাওয়া গেছে ‘স্ক্রিপচার’রূপে ইউরোপীয় আত্মাকে; অর্থাৎ কিনা, আমরা ইউরোপীয় ‘স্ক্রিপচার’ বা ‘রিলিজিয়াস বুক’-এর বাঙলা প্রতিনিধিরূপে অতঃপর ‘শাস্ত্র’কে পেয়েছি। মাঝ থেকে শাসনসাধন বা শাসনের হাতিয়ার যে শাস্ত্র, সে হয়ে গেল আরাধনার হাতিয়ার বা ধর্ম্মপুস্তক। এইভাবে প্রায় প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে, সমগ্র বাঙলাভাষার ক্ষেত্রে আত্মাবদল প্রক্রিয়া সাঙ্গ হল।
টীকা—
১। ‘শূদ্রধর্ম’, কালান্তর : রবীন্দ্রনাথ।
২। ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। ‘শ্রীশ্রী চণ্ডী’ : জগদীশ্চন্দ্র ঘোষ।
উদাহরস্বরূপ উল্লিখিত ‘ধর্ম্ম’ শব্দটির কথাই ধরা যাক। আত্মাবদল প্রক্রিয়ার চাপে ‘ধর্ম্ম’ ও তার বহুরৈখিক (ক্রিয়াভিত্তিক) অর্থ হারিয়ে Religion-এর প্রতিশব্দ মাত্র হয়ে গেল। অথচ কোথায় ‘ধর্ম্ম’ আর কোথায় Religion! ‘ধর্ম্ম’ হল ‘লোকধারক, শাস্ত্রানুশাসন বৈধকর্ম্ম, ন্যায়, নীতি, স্বভাব, প্রকৃতি, বিশেষ লক্ষণ ইত্যাদি, আর Religion হ’ল ‘human recognition of a personal God entitled to obedience’। বাঙলা ধর্ম্ম ও ইংরাজী Religion তো আদৌ এক বস্তু নয়। যেমন কিনা, বস্তুরও ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্মের গ্লানিও হয়, কিন্তু বস্তুর Religion হয় না, Religion-এর গ্লানিও হয় না। ধর্ম্ম ও Religion-এর মধ্যে এই যে বিশাল পার্থক্য ছিল, আত্মাবদল প্রক্রিয়ায় তার বিলোপ ঘটানো হল। কীভাবে?
‘ধর্ম্ম’-এর মত বাঙলা শব্দগুলির বর্ণ ও ধ্বনিগুলি যে ক্রিয়াভিত্তিক (বহুরৈখিক) অর্থধারণ করে, সে তো বলতে গেলে এক একটা জমিদারী, অন্য দিকে Religion-এর মত ইংরাজী শব্দগুলির ধ্বনি ও বর্ণগুলি কোন অর্থই ধারণ করে না; কিন্তু তাদের প্রত্যেকের বর্ণসমষ্টি একটি করে একরৈখিক অর্থ ধারণ করে, সেই বিচারে তারা বস্তুতই তাঁবুবাসী। তাই আত্মাবদল প্রক্রিয়ার কালে, যেহেতু ইংরেজ শাসক এবং যেহেতু তাদের ভাষার শব্দগুলি তাঁবুবাসী, বাঙলা ভাষার শব্দগুলিকেও তাদের জমিদারী কেড়ে নিয়ে তাঁবুবাসী করে দেওয়া হল; এমনকি তাদের শরীরেও হাত পড়ল— ‘ধর্ম্ম’ হয়ে গেল ‘ধর্ম’। বর্ণবিপর্য্যয় হয়ে গেলে যে অর্থবিপর্য্যয় ঘটে যায়, বাঙলা শব্দের এই স্বভাবের কথা বর্ণার্থ-অজ্ঞদের মাথায় আসেনি। কেননা, তাদের মাথায় ছিল উভয় ভাষার মধ্যে একপ্রকার সাম্য, ভাব বিনিময়ের জন্য যেটা ছিল জরুরী; আর বাঙলাভাষার মত প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষার শব্দগুলিকে ইংরেজী শব্দের মত তাঁবুবাসী করে দিয়ে সেই সৎকার্য্যটি সুসম্পন্ন করা হয়। ফলে, বাঙলাভাষা বাস্তবিকভাবে তার সাম্রাজ্য হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে আধুনিক বাঙলাভাষায় পরিণত হয়ে গেল। বাঙালীকে উদ্বাস্তু করে যত ক্ষতি করা হয়েছে, তার ভাষাকে উদ্বাস্তু করে তার চেয়ে কম ক্ষতিসাধন করা হয়নি।
আসলে, পাঠকেরও যে শ্রেণীবিভাগ সম্ভব, এবং সমগ্র পাঠককুলকে শ্রেণিবিভক্ত করে রাখা যেতে পারে, ইউরোপ তেমন ব্যাপার কল্পনাও করতে পারে না। ইউরোপীয় ধারণায় গ্রন্থপাঠ যে করে সেই পাঠক। বস্তুর ভর যেমন সর্ব্বত্র একই পরিমাণ থাকে, গ্রন্থের বিষয়বস্তুও সকল পাঠকের নিকট একই প্রকারে পৌঁছে দেওয়া হয়। কেননা, তাদের ধারণায়— একটা শব্দ বোঝাবে একটি বিষয় বা বস্তুকে, একটা বাক্য থেকে বেরিয়ে আসবে একটিই মানে। ব্যতিক্রম যদি কোথাও ঘটে, সেটা ব্যতিক্রম মাত্র। সাধারণভাবে একটা কথার দশরকম মানে হবে, দু’রকম পাঠক তার তিনরকম অর্থ বুঝবেন— এসব তাদের বাস্তববুদ্ধির সঙ্গে আদৌ মেলে না। ভাষা মাত্রেই তাদের বিচারে একরৈখিক অর্থবহনকারী, যেহেতু, তাদের নিজেদের ভাষা সেইরকম। দেহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিকশিত জাতিরূপে ইংরেজ সব ব্যাপারকেই দেহের দিক থেকে বুঝতে স্বস্তি বোধ করে, আত্মার দিক থেকে নয়। আধেয়ের চেয়ে আধারের দিকে, কন্টেণ্টের দিকে তার স্বাভাবিক নজর। তাই ভাষা ব্যবহারের ব্যাপারেও একরৈখিক (প্রতীকী) ভিন্ন অন্য কোনও রকমের ব্যবস্থার কথা ভাবা সম্ভব ছিল না তাদের পক্ষে। তাছাড়া, একরৈখিক ভাষার প্রতি পণ্যবাহী সমাজের স্বাভাবিক আস্কারা থাকে, কারণ সেটা তার ক্ষেত্রে অনেক বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।
কিন্তু আমাদের দেশে শাসকের ভাষাব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ভারতে যেমন সমুদ্র মন্থন করে কেউ পেত অমৃত, কারও ভাগ্যে জুটত শুধুই বিষ; তেমনি আমাদের শাস্ত্রমন্থনেও ছিল অধিকারীভেদ— উত্তম অধিকারী ও নিম্ন অধিকারী। শাস্ত্রগুলি সব লেখা হয় বহুরৈখিক অর্থ সমন্বিত ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়, ইংরেজীর মত একরৈখিক অর্থসমন্বিত প্রতীকী ভাষার নয়। যার মেধা কুলোয় কিংবা যাকে দীক্ষান্তে উপায়গুলি বলে দেওয়া হয়, সে বহুরৈখিক অর্থ গ্রহণ করে হয়ে যেত শাস্ত্রাধিকারী। আর যার মেধায় কুলোয় না, সে যে কোনও একরৈখিক অর্থ গ্রহণ করে থেকে যেত নিম্ন অধিকারী হয়ে। পাঠককূল তাই আমাদের শাস্ত্রানুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে নিম্ন অধিকারীর সঙ্গে ইংরেজের ঘনিষ্ঠতার কারণ প্রধানত দুটি!।
প্রথমত, যেহেতু শাস্ত্রের উত্তম অধিকারিগণই শাসনাধিকারীতে পরিণত হতেন, সমাজমনের শাসনের ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থায় এযাবৎ বিশেষ ছেদ পড়েনি। এমনকি মোগল যুগের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থাই কার্য্যত বলবৎ ছিল। নবাগত শাসকের সঙ্গে ওই শাস্ত্রাধিকারিগণের অসহযোগিতা ছিল প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। যে নিয়মে রামচন্দ্র বালীর চেয়ে সুগ্রীবকে কোল দেওয়া যুক্তিযুক্ত ঠাওরেছিলেন, সেই নিয়মেই নবাগত শাসক ইংরেজ নিম্ন অধিকারীকে কোল দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেছিল। এইরূপ সুবিধাবাদী প্রশ্রয়ের কারণে নিম্ন অধিকারিগণ নতুন শাসনাধিকারী রূপে ‘জজ পণ্ডিত’ পর্য্যন্ত বনে যান এবং উত্তম অধিকারিগণ ক্রমশ বাদ পড়ে যান, কেউবা নিম্ন অধিকারীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন(৫)। নিম্ন অধিকারী ও নবাগত ইংরেজের ঘনিষ্ঠতার অন্য কারণটি ইতোমধ্যে সুস্পষ্ট যে উভয়ের ভাষা ব্যবহার পদ্ধতি একরৈখিক হওয়ায় তাদের মনের মিল হতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। বহুরৈখিক সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষা থেকে একরৈখিক অর্থগ্রহণের নিকৃষ্টতাহেতু এতদিন নিম্ন অধিকারী ছিল অপাংক্তেয়, এখন সেই সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে উঠল। ইংরেজ তারই কাছ থেকে সংস্কৃত ও বাঙলায় লিখিত গ্রন্থগুলি জেনে বুঝে নিল— যা অগত্যা একরৈখিক হতে বাধ্য ছিল। রাজা যেভাবে বোঝে, নিজেদের ভাষাকে সেইভাবে কেটে ছেঁটে তার নিকট উপস্থাপন করার ব্যাপারে সে সময় কেমন প্রতিযোগিতা হয়েছিল, তা আমরা সবিশেষ জানি না, তবে সেই স্রোতে একসময় উত্তম অধিকারিগণের অনেকেই যে নিম্ন অধিকারীদের দলে নাম লিখিয়েছিলেন, তা প্রায় হলফ করে বলা যায়। ব্রিটিশ-ভারতের আদি আইন শাস্ত্র ‘জন্তু কোড্’ নামটুকু থেকেই তা প্রমাণ করে দেওয়া যায়।
যাই হোক, এর ফলে নিম্ন অধিকারী যে কেবল সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে উঠল তাই নয়, তার ও তার নতুন প্রভুর একরৈখিক অর্থসমন্বিত প্রতীকী ভাষা পদ্ধতিই দুনিয়ার একমাত্র ভাষা পদ্ধতি রূপে ঘোষিত হয়ে গেল। বহুরৈখিক ভারতীয় ভাষাগুলির কেবলমাত্র একরৈখিক অর্থ গৃহীত হতে লাগল, এবং এইভাবে গৃহীত হতে হতে একদিন সমগ্র বাঙলা ভাষাই ইংরেজীর মত প্রতীকী ভাষায় পরিণত হয়ে গেল। আর আমরাও ধীরে ধীরে ভারতীয় বাঙলার বদলে, বলা ভাল, ইউরোপীয় বাঙলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম এবং আমাদের আদি বাঙলাভাষা যা বহুরৈখিক অর্থসমন্বিত ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা রূপে আবির্ভূত হয়েছিল সেকথা আমরা একদিন বেমালুম ভুলে গেলাম। এখন, আমাদের দেশ থেকে ইংরেজ চলে গেছে, কিন্তু আমাদের ভাষা থেকে তার বিদায়পর্ব্ব সমাধা হতে সম্পূর্ণই বাকী। বলতে কি, আমাদের ভাষা বিশেষজ্ঞ ও নিম্নাধিকারী সাহিত্যিকদের কৃপায় বাঙলা ভাষার ভিতর ইংরেজের ঔপনিবেশিক সিংহাসন বহাল তবিয়তে বি-রাজ করছে এবং তার শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা ছদ্মবেশী বাঙলা ভাষা নিয়ে ঘর করছি, যে বাঙলা ভাষার রয়েছে বঙ্গীয় দেহ ও ইউরোপীয় আত্মা। তাই নিয়েই আমরা বড়াই করছি, দাবী-দাওয়া করছি, একই দুরবস্থায় ভুক্তভোগী হিন্দী ভাষার সঙ্গে ঘরোয়া কোন্দল করছি। কেউ বা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এমন বাঙলারূপী ইংরেজী শেখার চেয়ে বরং সরাসরি ইংরেজী শেখাই ভাল।
তা সে যাই হোক, ইংরেজের উপনিবেশের প্রারম্ভকালে বাঙলা ভাষার ঐরূপ আত্মাবদল প্রক্রিয়া সাঙ্গ হবার পর, ইংরেজের সঙ্গে আমাদের ভাষাবিনিময়ের পথটা সুগম হল ঠিকই। কিন্তু বহুরৈখিক অর্থসমন্বিত ক্রিয়াভিত্তিক সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হওয়ায় আমরা আমাদের অতীত থেকে, ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যের কেবলমাত্র একরৈখিক অর্থ বোঝা হতে লাগল। আমরা শিখলাম আমাদের পূজ্যপাদ হনুমান মানে নিকৃষ্ট এক জানোয়ার monkey, দেবতাকে জানলাম God বলে, নাগ ও সর্পকে চিনলাম Serpent-এর অনুরূপে, সীতাকে বুঝলাম হেলেন অফ ট্রয়ের অনুকরণে [ হায়! কোথায় অযোনিসম্ভবা সীতা, আর কোথায় হেলেন! ], কুরুক্ষেত্রকে জানলাম ওয়াটার্লুর সমগোত্রীয় বলে, রামায়ণ-মহাভারতকে বললাম mythology, কামসূত্রকে বললাম Sexology(৬)। আর, আমাদের নিজেদের ভালমন্দ বোধ দিয়ে নয়, খ্রীষ্টান বৃটিশের ভালমন্দ বোধের মাপকাঠীতে ঐগুলিকে বিচার করতে বসলাম, যেহেতু ব্রিটিশই রাজা, এবং অতএব, তার সবই শ্রেষ্ঠ, আর আমাদের ধারণাতেও ততদিনে তার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত। ফলত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের বিশাল পৌরাণিক ইতিহাসের অমৃত কলস পরিণত হয়ে গেল এক ঘড়া গঙ্গাজলে, পবিত্র এবং দূষিত, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, আমরা আত্মপরিচয়হীন হয়ে গেলাম। মার্ক্স ও রবীন্দ্রনাথ, এই দুই মনীষীই, এই ‘আত্মবিচ্ছেদ’কেই ভারতবাসীর সমস্ত দুর্দ্দশার কারণ বলে চিহ্নিত করে গেলেন(৭)।
টীকা—
৪। মাও সে তুঙের রচনা থেকে।
৫। ‘জজ পণ্ডিতের কথা’ : পূর্ণেন্দুনাথ নাথ [ ‘দেশ’ – ১৯.০৯.১৯৯২ ]
৬। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্বের সাহায্যে জানা গেছে হনুমান, দেবতা, নাগ, সর্প প্রভৃতি যথাক্রমে Monkey, God, Serpent, Snake নয়, আদৌ নয়।
৭। দ্রষ্টব্য ‘ভারতে ব্রিটিশ শাসন’ : মার্ক্স; ও ‘সভ্যতার সঙ্কট’ : রবীন্দ্রনাথ।
এতদিন পরে সে ‘আত্মবিচ্ছেদের ছিন্নসূত্রগুলি’ জোড়া দেবার সুযোগ এসেছে আমাদের হাতে। পাওয়া গেছে বেদপুরাণাদির বহুরৈখিক অর্থগ্রহণের উপায়ের সুলুক-সন্ধান, যার সাহায্যে ঐ ছিন্নসূত্রগুলি এক এক করে ধীরে ধীরে জোড়া সম্ভব এবং আমাদের আত্মপরিচয় ফিরে পাওয়া সম্ভব। এর ফলে বাঙলা ভাষার সাথে সাথে সমস্ত ভারতীয় ভাষায় ভারতাত্মার পুনরাধিষ্ঠান যেমন সম্ভব হবে, ইউরোপীয় আত্মার ভূত বিতাড়নও সম্ভব হবে, ভাষাকে মুক্ত করা যাবে ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে। বাঙলা সহ সমস্ত ভারতীয় ভাষা এভাবেই প্রকৃতার্থে স্বাধীন ও মুক্ত হতে পারবে। ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে এভাবেই একটি জাতিকে তার নিজস্বতা নিয়ে উঠে আসতে হয়। ঋষি বঙ্কিমের একটি বিধানকে এক্ষেত্রে আমরা যুগোপযোগী করে বলতে পারি, ‘একমাত্র এইভাবেই, বিশ্বের জাতিসমূহ সর্ব্বার্থে স্বাধীন ও মুক্ত হয়ে পরস্পরকে বুঝতে ও প্রভাবিত করতে পারে, এবং সম্মিলিত ভাবে বিশ্বশক্তিগুলিকেও প্রভাবিত করতে পারে। অন্যথায় মানব জাতির কোনও আশা নেই।’(৮)
সুতরাং ‘আত্মবিচ্ছেদের ছিন্নসূত্রগুলি’ এবার জোড়া দিতে হবে। কিন্তু কাজটা একজনের নয়, এক দিনেরও নয়। এক একটি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সব মিলিয়ে, সে এক সুবিশাল কাহিনী। এর মধ্যে, ‘হাওয়া ৪৯’-এর সম্পাদক আমাকে বলেছেন, বাৎস্যায়নের কামসূত্রের প্রকৃত স্বরূপটিকে আজকের ভাষায় ভাষান্তর করে দিতে। তাহলে, ‘কামসূত্র’ কেমন Sexology, সেই ‘আত্মবিচ্ছেদের ছিন্নসূত্র’ এবার জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করা যাক।
দুই—
আমার ছিল দু’বস্তা ধান, আপনার একটা গরু। আমরা বিনিময় করলাম। শাস্ত্রমতে, এই বিনিময় আমি আপনি করিনি। আপনার ছিল ধানের প্রতি কামনা, আমার কামনা ছিল গরুর প্রতি। কাম ছিল আমার অন্তরে, কাম ছিল আপনার অন্তরেও। অর্থাৎ ‘কাম’ আমার আপনার দুজনের অন্তরে বিদ্যমান থেকে ঐ লেনদেন ঘটিয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় মনীষা এইরূপ আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখতে অভ্যস্ত ছিল। তাই শাস্ত্র বলেন— ‘কে দিয়েছে? কে নিয়েছে? কামই দিয়েছে। কামই নিয়েছে।’— (ঋকবেদ)। আর বিনিময়যোগ্য ঐ বস্তুগুলি আমাদের মনে ‘কাম-উদিত’ করে বলে তারা কামোদিতি (>commodity) পদবাচ্য। উদিত কামকে না হয় চেনা গেল, কিন্তু রতি কই?
ধরা যাক, আপনি কর্ম্মজগৎ সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞ এবং নতুন এক পরিকল্পনার আবিষ্কারক। আর আমরা কয়েকজন আপনার পরিকল্পনার কথা শুনেছি এবং তা কাজে রূপায়িত করলে কীরূপ অবাকফসল উৎপাদিত হবে তার স্বপ্নে বিভোর। এই ক্ষেত্রে আপনার যদি আমাদের কর্ম্মশক্তির প্রতি, এবং আমাদের যদি আপনার পরিকল্পনার প্রতি কামনা জন্মায়, তাহলে সরল লেনদেনের মাধ্যমে এইরূপ কামচরিতার্থ হওয়ার কোনও উপায় নেই। তার জন্য আপনার সঙ্গে আমাদেরকে কর্ম্মে রত হতে হবে। যে নিয়মে ‘গত হতে থাকা’কে ‘গতি’ বলায় হয়, সেই নিয়মেই ‘রত হতে থাকা’কে ‘রতি’ বলে। অর্থাৎ কিনা, এইরূপ কামের ‘জ্ঞানাংশ’ ও ‘কর্ম্মাংশ’ দুটিই বিদ্যমান, যাদের যথাক্রমে ‘কামোন্মাদনা’ বা ‘কর্ম্মোন্মাদনা’ এবং ‘কামসম্পাদনা’ বা ‘কর্ম্মসম্পাদনা’ বলে। বস্তুত ‘কামে’ আর ‘কর্ম্মে’ কোনও প্রভেদ নেই বলেই ভারতের বেশীর ভাগ প্রাদেশিক ভাষায় কর্ম্মের প্রতিশব্দই কাম। কর্ম্মোন্মাদনাই (=প্রেমভাব) ‘মদন’ এবং কর্ম্মসম্পাদনাই (প্রেমকর্ম্ম) ‘রতি’ শব্দে পরিকীর্ত্তিত হয়েছে। যাঁরা জীবনে অন্তত একবারও কোনও নতুন পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য কিছু লোকলস্কর বন্ধুবান্ধব নিয়ে কর্ম্মোন্মাদনায় মত্ত ও রত হয়েছে, এ ব্যাপার তাঁদের পক্ষে অনায়াস বোধগম্য সন্দেহ নেই।
কিন্তু এই যে আপনার সঙ্গে আমরা প্রেমে (প্রেমভাব ও প্রেমকর্ম্ম দুটোতেই) মত্ত বিভোর হয়ে কাম চরিতার্থ (Job Satisfaction লাভ) করলাম, এর ফসলের মালিক কে হবে? আগেভাগেই তাহলে আমাদের সঙ্গে আপনার একটা চুক্তি বা Contract হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমরা তো জানি যাকে ‘Carry out’ করতে হয় বা বহন করতে হয় তাকে ‘Contract’ বা ‘বিবাহ’ই বলে। তবে এরূপ বিবাহের বা Contract-এর রূপায়ণ সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন ‘গার্হস্থ্য বিধানে ক্রিয়ানুষ্ঠান’ চলে। পুরাণাদি সাক্ষ্য দেয় যে কেবলমাত্র দক্ষযজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হবার পরবর্ত্তী কাল থেকে ভারত সমাজে এইরূপ ‘স্ত্রী পুরুষ ধর্ম্মানুসারে গার্হস্থ্য বিধানে ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রচলন হয়।’(৯) কারণ তার আগে সমাজের ‘অর্দ্ধাংশ নারী’ (স্ত্রী, কর্ম্মিজনগণ) ও ‘অর্দ্ধাংশ পুরুষ (জ্ঞানী, পরিচালক) মূর্ত্তি ধারণ’ করেনি। তাই গার্হস্থ্যবিধানে ক্রিয়ানুষ্ঠানেরও উপায় ছিল না, আর তাই বিবাহেরও প্রচলন হয়নি। কারণ বিবাহের বা চুক্তির প্রচলন তখনই হওয়া সম্ভব, যখন বেদের মর্য্যাদা বা জ্ঞানের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে’; অর্থাৎ কিনা জ্ঞানীই জ্ঞানের মালিক একথা সমাজ স্বীকার করে নিয়েছে। আধুনিকভাষায় একে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস বলা হয়ে থাকে। পুরাণাদি সাক্ষ্য দেয় দক্ষযজ্ঞের পর থেকে বিবাহের সূত্রপাত অর্থাৎ চুক্তি করে লোকজন নিয়ে কাজকর্ম্ম করার শুরু তখন থেকেই।
তা সে যাই হোক, আপনার জ্ঞানের মালিক আপনিই, সমাজ নয়, এই আদি ব্যক্তি মালিকানা অর্থাৎ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস সমাজ স্বীকার করে নিয়েছে বলে আপনিই এখন ‘শঙ্কর’তুল্য। এখন কর্ম্মী জনগণের সঙ্গে চুক্তি (বিবাহ) বন্ধনে যাওয়ার আগে আপনাকে প্রথমেই ‘মদনভস্ম’ করে ফেলতে হবে, তার পরে আসবে বিবাহের কথা, তারও পরে বিবাহোত্তর কামচর্চ্চার কথা এবং উৎপাদিত ফসলের মালিকানার কথা।
আগেই বলা হয়েছে, কাম দুই প্রকার, কর্ম্মোন্মাদনা বা ‘মদন’ এবং কর্ম্মসম্পাদনা বা ‘রতি। এই মদনকে অর্থাৎ কর্ম্মোন্মাদনাকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিতে হবে। অর্থাৎ কিনা প্রেমভাব থাকবে না, কিন্তু প্রেমকর্ম্ম থাকবে, রতি থাকবে। কী করে আপনি আমাদের কর্ম্মোন্মাদনা (মদন) কে ভস্ম করবেন? খুব সহজ। সব পরিচালকই করে থাকেন। আপনি শুরুতেই ঘোষণা করবেন— ‘তোমরা আসবে, যেমন কাজ করতে নির্দ্দেশ দেব, করবে, কী হচ্ছে না হচ্ছে তা তোমাদের ভাবতে হবে না; পরিকল্পনা আমার, আমিই বুঝব তার ভালমন্দ; পরিকল্পনাকে ভালবেসে কর্ম্মোন্মাদনায় তোমাদেরকে মত্ত হতে হবে না, খাটবে, পয়সা নেবে, চলে যাবে।’ এ আর কিছুই নয়, কেবল ‘মা ফলেষু কদাচন’ বলা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— ‘কর্ম্ম থেকে ফলাকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া লইলে কর্ম্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া দেওয়া হয়’(১০)। আপনি কেবল সেটুকু করবেন। ব্যাস, দেখবেন ‘মদনভস্ম’ হয়ে গেছে। বেঁচে থাকবে কেবল ‘রতিবিলাপ’। কর্ম্মী জনগণ এরপর আসবে, খাটবে, মজুরী নেবে, চলে যাবে। পরিচালকের প্রতি, তার পরিকল্পনার প্রতি, তাদের প্রেমভাব নেই, এক ধরণের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিতে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। উৎপাদিত ফসলের প্রতি তার দাবীর কথা বলার কোনও উপায়ই নেই তার হাতে। ‘মদনভস্ম’ করে তার গোড়া মেরে দেওয়া হয়েছে। এই জন্য বিবাহের আগেই আপনাকে ‘মদনভস্ম’ করে ফেলতেই হবে। তার পরে হবে বিবাহ, তার পরে হবে কামচর্চ্চা। অন্যথায়, পরে উৎপাদিত বস্তুর ওপর থেকে তাদের অধিকারের দাবীকে নাকচ করা আপনার পক্ষে মুশকিল হবে।
মার্ক্স সাহেব পণ্য উৎপাদনের আদি রহস্য খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে প্রাচীন ভারতে পৌঁছে যান এবং দেখতে পান যে, ‘In the Primitive Indian Community there is social division of labour without production of commodities’(১১)। কিন্তু Social division of labour বলতে যে জ্ঞানী কর্ম্মী বিভাজন করা এবং তারপর ‘মদনভস্ম করাতেই যে সত্যিকারের পণ্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল, সে তথ্য তিনি জানতেই পারেন নি। কারণ তাঁর জানা ছিল না, ভারতে প্রেম ছিল দুই প্রকার— সকাম প্রেম ও নিষ্কাম প্রেম। সকাম প্রেম হল সেই বস্তু যেখানে মদন ও রতি উভয়েই বিদ্যমান। আর নিষ্কাম প্রেম হল যেখানে মদন ভস্মীভূত, অস্তিত্ব কেবল রতি বিলাপের। কামহীন নিষ্কাম প্রেমীর ক্লান্তিকর যান্ত্রিক রতিবিলাপের অনিবার্য্য ফসল হল পণ্য। পরিকল্পনাকারী-পরিচালক-জ্ঞানী যার মালিক। এই সেই কারণ, যে জন্য ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে সকাম প্রেমের ঝুড়ী ঝুড়ী নিন্দা এবং নিষ্কাম প্রেমের গৌরব বিঘোষিত হয়েছে। অথচ, একথা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হয় না যে, যে প্রেমে মদন নাই কেবল রতির অস্তিত্ব আছে, সে ত একপ্রকার অশ্লীল এক যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির ক্লান্তিকর প্রক্রিয়া মাত্র, যাতে পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের প্রতি কোনরূপ মানসিক আকর্ষণ থাকে না। কর্ম্মী আসে কাজ করে চলে যায়, মালিককে বা পরিচালককে কিংবা তার পরিকল্পনাকে ভালবাসে না, ভালবাসতে চাইলেও তার উপায় নেই, তাই সে নিস্পৃহ। আর মালিক বা পরিচালকও কর্ম্মীদের ভালবাসে না, ভালবাসতে চাইলেও তার উপায় নেই— উৎপন্নে ভাগ চেয়ে বসে যদি, তাই সেও নির্ব্বিকার থাকে। ফলত কারোরই কাম চরিতার্থ (Job Satisfaction) হয় না। অথচ জ্ঞানের মালিকানা মেনে নিলে, ব্যক্তি মালিকানার দিকে হাঁটতেই হয়, পণ্য উৎপাদনের জন্য নিষ্কাম প্রেমের চর্চ্চা করতেই হয় এবং Job Satisfaction-এর আশা ছাড়তেই হয়। জীবিকা থেকে তখন কেবল রসদই বেরোয়, রস বেরোয় না। ফলে এক অদ্ভুত পণ্যসম্পন্ন বিপন্ন জীবনের উপলব্ধি ঘটে মানুষের। তার থেকে পরিত্রাণের প্রত্যাশায় বর্ত্তমান যুগের কোনও কোনও ম্যানেজমেণ্ট আবার মদনকে না চিনেই ‘মদন’কে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। এবং হয়ত সেটাই হবে ভবিষ্যতের একমাত্র পথ।
অথচ এতদিন যে আমরা জানতাম, নিষ্কাম প্রেম মানে রতি ব্যাপারটাই বাদ, তার অর্থ কী? তার অর্থ এই যে, স্ত্রী (কর্ম্মিজনগণ)-কে বোঝানো, যে সন্তানের (উৎপাদনের) প্রতি তার যেন কোনও কামনা না থাকে, সন্তান (উৎপন্ন) কেবল স্বামীর (পরিচালকের)। কিন্তু এর ফলে স্ত্রীর (কর্ম্মিগণের) কামচর্চ্চার ইচ্ছা উবে যাবে, কেননা এ তো সরাসরি মদনভস্ম, প্রতারণা। ঠিক এই জন্যই একদিন ভারতে (কর্ম্মী জনগণের) কামচর্চ্চা বিষয়ক গ্রন্থ লিখতে হয়, মন্দির গাত্র ভরিয়ে ফেলতে হয় সঙ্গম মুদ্রায়। ঠিক যেভাবে শিবকে মেরে শিবপূজা, নারায়ণকে মেরে নারায়ণ পূজা, গান্ধীকে মেরে গান্ধী পূজা ও তাঁদের মূর্ত্তী ও তৎসংক্রান্ত ডিসকোর্সে সমাজকে ভরিয়ে ফেলে পুরোহিততন্ত্র, সেইরকম। তবে ভারতবর্ষে ‘অনঙ্গরঙ্গ’, ‘কন্দর্পচূড়ামণি’, ‘রতিরহস্য’, ‘পঞ্চসায়ক’, ‘রতিরত্নপ্রদীপিকা’, ‘কামসূত্র’ ইত্যাদি নামে যত গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেগুলির বিশেষত্ব এই যে, যে গ্রন্থ যত অর্ব্বাচীন তাতে তত বেশী মানবদেহ বিষয়ক কামচর্চ্চা প্রকটিত হয়েছে, অর্থাৎ, বহুরৈখিক পদ্ধতিতে লিখিত আদি কামশাস্ত্র ক্রমান্বয়ে একরৈখিক দিকে এগিয়েছে। সেইজন্যই প্রতীকী ভাষা পদ্ধতির এই যুগে ওইগুলোকে Sexology বিষয়ক গ্রন্থ বলে ভ্রম হয়। তা হোক, এখনই সে সব বিষয়ে আমরা যাব না। কারণ, এখনও বিবাহকার্য্য সমাধা হতে বাকী।
টীকা—
৮। মীর মোশাররফ হোসেনের ‘আত্মজীবনী’ গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেন।
৯। দ্রষ্টব্য : ‘হরিবংশ পুরাণ’।
১০। ‘নববর্ষ’ : রবীন্দ্রনাথ।
১১। Marx : ‘Capital’ – Vol.1 : Page- 49
বিবাহের আগে আপনাকে দেখে নিতে হবে কন্যা কামকলা কী কী জানে? দেখতে হবে সে ৬৪ কলা পারদর্শী কিনা, তার মধ্যে ‘কর্ম্মাশ্রয় চতুর্ব্বিংশতিকলা’ ছাড়াও অন্তর্নিবিষ্ট ৫১৮ কলা জানার ব্যাপার আছে যার ভিতরে “কর্ম্মাশ্রয় ও দ্যূতাশ্রয় কলাগুলি প্রায়শই একটু ‘আগপাশ’ গিয়াছে” তার খবরও জানতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন কামশাস্ত্রমতে আপনাকে দেখতে হবে কন্যা (=যে সকল কর্ম্মীকে নিয়ে আপনি কর্ম্মে রত হবেন, তারা) যন্ত্রমাতৃকা জানে কি না, দেশভাষাবিজ্ঞান জানে কি না, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ জানে কি না, ধাতুবাদ জানে কি না, বাস্তুবিদ্যা-তক্ষকর্ম্ম-তক্ষণকর্ম্ম ইত্যাদি জানে কি না। যন্ত্রমাতৃকা জানা মানে— রথ শকট ঘানিযন্ত্র আখপেষাই যন্ত্র রণতরী রক্ষিতরী ব্যোমযান পূষ্পকরথ আগ্নেয়রথ বানরধ্বজরথ গর্দ্দভযান পুষ্করযান বিধ্বংসিনী তরণী— ইত্যাদির নির্ম্মাণবিধি জানা (Mechanical); বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ জানা বলতে, বৃক্ষের রোপণ-পুষ্টি এবং চিকিৎসা করতে জানা (Agro Science)। আর ধাতুবাদ মানে ক্ষেত্রবাদ অর্থাৎ সেটি মৃত্তিকা প্রস্তর রত্ন ও ধাতু প্রভৃতির পাতন ঢালাই শোধন মেলন ইত্যাদি (Metallurgy & Mining)। বাস্তুবিদ্যা হল গৃহনির্ম্মাণকার্য্য (Civil Engineering)। আর তক্ষকর্ম্ম হল বয়নকৌশল, কার্পাস থেকে সূতা কাটা ইত্যাদি এবং তক্ষণ হল কার্পেণ্টার বা ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ। হ্যাঁ। শাস্ত্রানুসারে আপনাকে বিবাহের আগে দেখে নিতে হবে যে কন্যার সঙ্গে (যে সকল কর্ম্মীর সঙ্গে) বিবাহ (চুক্তি) হবে তারা ইত্যাকার ৬৪ কলা জানে কি না।
কী বিপজ্জনক! এই কামসূত্র অনুসারে সত্যিই যদি এ যুগের বিয়ের পাত্রী খুঁজতে হয়, তাহলে তো পাত্রীই পাওয়া যাবে না। কেননা তাহলে তো ছুতোরের কাজ থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পর্য্যন্ত সবই জানতে হবে পাত্রীকে। তা কি কখনও সম্ভব? এ যুগের যে সকল পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণ বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রকে কেবলমাত্র Sexology-র গ্রন্থ ভাবতে অতি ব্যাকুল, তাঁরা একবারও কেন যে এই প্রশ্ন তোলেন না, বোঝা মুশকিল। অথচ, প্রশ্নটি তুললেই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারতেন যে এই ‘কন্যা’ শব্দটি কর্ম্মী জনগণকে বোঝাচ্ছে এবং এই কামসূত্র মূলত কাজকামের সূত্র।
ধরা যাক, ঐরকম ৬৪ কলা জানা কন্যা অর্থাৎ কর্ম্মী জনগণ পাওয়া গেল। এবার বিবাহ (=চুক্তি) সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু কোন মতে বিবাহ হবে? কৌটিল্যের যুগে এসে আট প্রকার বিবাহ বিধির কথা পাচ্ছে।
(১) ব্রাহ্মবিবাহ— ‘যে বিবাহে কন্যাকে অলংকৃত করিয়া বরের হস্তে প্রদান করা হয়’ অর্থাৎ কর্ম্মী জনগণের সমস্ত দায়িত্ব পরিচালকের, সমাজ বসে এইভাবে নির্দ্দেশ দিয়ে ভাগ করে এক এক জন পরিচালকের হাতে বাকী জনগণোকে সম্প্রদান করে। এই প্রথা অতি প্রাচীন ও আদি। যৌথ সমাজের শেষ পাদে এইরূপ বিবাহের প্রচলন হয়। এতে উৎপাদন বণ্টনে বৈষম্য নেই।
(২) প্রাজাপত্য বিবাহ— ‘এই বিবাহে কন্যা ও বর একসঙ্গে মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া পরিণীত হয়’ অর্থাৎ কর্ম্মী জনগণ স্বেচ্ছায় এইরূপ চুক্তি করে। এটির সূত্রপাত দক্ষ প্রজাপতির প্রতিষ্ঠা লাভের কালে, যখন সতী শিবের বারণ সত্ত্বেও দক্ষযজ্ঞে সামিল হয়। সমাজ বিকাশের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে এইরূপ সামাজিক চুক্তির প্রতিষ্ঠা।
(৩) আর্য্য বিবাহ— ‘যে বিবাহে বরের দিক হইতে দুইটি গাভী গ্রহণ করিয়া কন্যা প্রদত্ত হয়’ অর্থাৎ সমাজ বিকাশের তৃতীয় পর্য্যায়ে এইরূপ সামাজিক চুক্তির প্রতিষ্ঠা যখন, কর্ম্মী জনগণ আর মুক্ত নয়, কারও না কারও এখতিয়ারভুক্ত। যার এখতিয়ারভুক্ত সেই পিতামাতা।
(৪) দৈব বিবাহ— ‘যে বিবাহে যজ্ঞবেদী মধ্যে স্থিত ঋত্বিকের নিকট কন্যা প্রদত্ত হয়’ অর্থাৎ যখন পরিচালক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ শুরু করে দিয়েছে তখন সেই অবস্থায় যে কর্ম্মী জনগণকে তার নিকুট সরবরাহ করা হয়, আধুনিক ভাষায় এইরূপ কন্যার পিতাকে ‘লেবার-সাপ্লায়ার’ বলে।
(৫) গান্ধর্ব্ব বিবাহ— ‘যে বিবাহে বর ও কন্যা স্বেচ্ছায়, পিতামাতার অভিমত না লইয়া, একে অন্যকে গ্রহণ করে’ অর্থাৎ এইরূপ সামাজিক চুক্তি সম্ভব হয় তখনই যখন ভূমিদাস পালায়, পালিয়ে হাজির হয় শহরে, কারও এখতিয়ার সে মানে না তখন। গান্ধর্ব্ববিবাহ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি।
(৬) আসুর বিবাহ— ‘যে বিবাহে বর কন্যার পিতাকে বা কন্যাকে শুল্কধন দিয়া কন্যা গ্রহণ করে’ অর্থাৎ এইরূপ সামাজিক চুক্তিকেই দাসপ্রথা বলে।
(৭) রাক্ষস বিবাহ— ‘যে বিবাহে বলাৎকারে কন্যা গ্রহণ করা হয়’ অর্থাৎ আরেক প্রকারের কঠোর দাসপ্রথা।
(৮) পৈশাচ বিবাহ— ‘যে বিবাহে সুপ্ত কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করা হয়’ — এ এমন এক দাসপ্রথা যা আফ্রিকার নিগ্রদের সঙ্গে ইউরোপ বহুদিন করেছে।
এই আট প্রকার চুক্তির মধ্যে কোনও এক প্রকার চুক্তি সেরে ফেলতে হবে কর্ম্মীদের সঙ্গে। তারপর কর্ম্মে রত হওয়ার পালা, ফসল উৎপাদনের পালা, নিষ্কাম প্রেমচর্চ্চার পালা। — না না, নতুন কিছু আপনি করছেন না; ভারত সরকার এখনও আট রকম contract form-ই ব্যবহার করে থাকে।
প্রকৃতবিচারে সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞের রীতি পদ্ধতিই সমাজের কাঠামো কেমন হবে তা নির্দ্ধারণ করে। সেই রীতি-পদ্ধতিতে নিষ্কাম প্রেমচর্চ্চাই ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক সমাজ সৃষ্টির মূলে। মদনভস্ম করে ফেলার পর যে কামহীন নিষ্কাম প্রেম, তার খপ্পরে পড়া অর্থাৎ রতিবিলাপের আবর্ত্তে পড়ে যাওয়া, যে কতখানি নির্ম্মম কঠোর একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিমূলক ক্লান্তিকর মৌলবাদী যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, তা কেবল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে পারেন কারখানা শ্রমিক, কিছু সরকারী কর্ম্মচারী, প্রেম খোয়ানো দম্পতি, বেশ্যা, এবং আরও অনেকেই যারা একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তির নিগড়ে এমনভাবে আবদ্ধ যে, সৃষ্টিশীল কোনও কিছু করার সুযোগ বা অধিকার তাঁদের হাতে নেই। কারণ, এতে পরিচালক (স্বামী/পুরুষ) ও কর্ম্মী জনগণের (স্ত্রী’র) পরস্পরের প্রতি কোনও রকম মানসিক আকর্ষণের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট থাকে না। বলতে গেলে, এরূপ নিষ্কাম প্রেমচর্চ্চার আদর্শ স্থান বেশ্যালয় ও সমস্ত সরকারী সংস্থা। বলতে গেলে, অবিরাম রতিবিলাপই সরকারী সংস্থাগুলির লোকসানের মুখ্য কারণ। সেই জন্যই কোনও কোনও দেশের ম্যানেজমেণ্ট এখন ‘Hire and fire’ নীতি অনুসরণ করে থাকে। খ্রীষ্টিয় ভাবনার দিক থেকে ভাবলেও নিষ্কাম প্রেমের চেয়ে অশ্লীল শব্দ আর কিছু হতে পারে না। তথাপি সত্য এই যে, ভারতবর্ষকে একদিন নিষ্কাম প্রেমের চর্চ্চা করতে হয়েছিল। অন্যথায় কর্ম্মী জনগণ (স্ত্রী) পরিচালকদের (পুরুষের) সঙ্গে প্রাজাপত্য বিবাহের দ্বারা মিলিত হয়ে যে উৎপাদন যজ্ঞ করত, সেই যজ্ঞ ফলের প্রতি তার অধিকার তারা ছেড়ে দিত না, জ্ঞান ও জ্ঞানীর, বেদ ও বেদীর (পুরুষের) মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হত না, পণ্য সৃষ্টি হত না, ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক সমাজ সৃষ্টি হত না, তথাকথিত ‘বর্ব্বর’ যুগ অতিক্রম করে সমাজ ‘সভ্য’যুগে পাড়ি জমাতে পারত না। আজও ভারতীয় আইনে সন্তান কেন পিতার, মাতার নয়, সে রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু এখানেই। শুধু তাই নয়, নিম্নাধিকারীর হাতে শাস্ত্রানুশাসন চলে যাওয়ায়, পরিচালক ও কর্ম্মীগণের সম্পর্কের সমস্ত উত্তর-দায়িত্ব এখন বহন করে মরছে প্রায় প্রতিটি ভারতীয় দম্পতি। কার পাপ, কে তার বোঝা বইছে! যে আচার সমুদয় পালন করার কথা ছিল পরিচালক ও কর্ম্মিগণের, সে আচার পালন করে চলেছে স্বামী-স্ত্রী। (১২)
তিন—
Productivity Council, Export Promotion Council ইত্যাদি নামে ভারত সরকারের কয়েকটি সংস্থা আছে। সংস্থাগুলি উৎপাদন-বৃদ্ধি, ও রপ্তানী-বৃদ্ধির কাজ করে থাকে। কেবলমাত্র ভোগের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই চলে না। তাছাড়া সেরূপ উৎপাদন পণ্য পদবাচ্য নয়। রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য ‘যে যায়’ (‘গো’/বঙ্গীয় শব্দকোষ দ্রষ্টব্য) উৎপাদকের ভোগের নিমিত্ত পড়ে থাকে না, তেমন পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই প্রয়োজন, অর্থাৎ কিনা ‘গো’-বর্দ্ধন প্রয়োজন। আর ঐরূপ গোবর্দ্ধনের জন্য গোপ গোপী গোপালদের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া জরুরী, অন্যথায় গোবৎস্য উপাদন বাড়বে কী করে! তবে হ্যাঁ! স্বয়ং নগদ-নারায়ণ যদি Black Money (শ্রীকৃষ্ণ) রূপে গোবর্দ্ধনধারী হয়ে যান, তাহলে প্রজাদের কেবল হর্ষবর্দ্ধন হয় না, তাদের রাজ্যশ্রীও ফিরে আসে। ভারতবর্ষে একদিন সেইরূপ যথার্থ গোবর্দ্ধন (Industrial Revolution) থেকে রাজ্যবর্দ্ধন (Imperialism), হর্ষবর্দ্ধন ও রাজ্যশ্রীর জন্ম হয়েছিল। সেই বৌদ্ধযুগে গোবৎস বৃদ্ধির যে বিদ্যা, তার চর্চ্চা করার জন্য যে Productivity Council ছিল, তারই নাম বাৎস্যায়ন। বর্ত্তমান Productivity Council-এর যেমন বইপত্র বিধান নিদান রয়েছে, বাৎস্যায়নেরও ছিল। তবে এই council-এর আধুনিক চেহারায় নয়, ক্রমান্বয়ে পেছন পানে হেঁটে হেঁটে ঐরূপ সংস্থার আদিরূপ পৌঁছে তবেই বাৎস্যায়নকে জানতে বুঝতে হবে। আদি রূপ পৌঁছে যাদের সাক্ষাৎ মেলে, তাদের অন্তত একজনকে হাজির করা যাক।
West Bengal State Electricity Board বা WBSEB-কে সবাই চেনেন। এর একেবারে নীচে খালাসী, তার পরের স্তরে ওয়্যারম্যান ইলেক্ট্রিসিয়ান, তার উপরের স্তরে সুপারভাইজার, ক্লার্ক অব ওয়ার্ক্স, তার উপরের স্তরে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ারএবং সবশেষে চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার। কর্ম্মী সংখ্যা নীচের দিকে যত বেশী, উপরের দিকে তত কম এবং শিখরে একজন মাত্র। সংস্থা বা সঙ্গঠন মাত্রেরই এই চেহারা – বড় স্তরের পর ছোট আকারের স্তর, তার ওপর আরও ছোট স্তর। স্তরে স্তরে বা পর্ব্বে পর্ব্বে এইরূপে বিন্যস্ত বলে প্রাচীন ভারতে সংস্থা মাত্রকেই ‘পর্ব্বত’ বলা হত। WBSEB সেই হিসাবে একটি পর্ব্বত মাত্র। কিন্তু যেহেতু সে বিহার ওড়িশা ডিভিসি থেকে বিদ্যুৎ কেনে এবং আমাদেরকে বিক্রী করে থাকে, তাই তার দুটো পক্ষ আছে— বিদ্যুৎ বিক্রেতা পক্ষ, যাদের কাছ থেকে সে কেনে; এবং বিদ্যুৎ ক্রেতা পক্ষ, যাদেরকে সে বিদ্যুৎ বিক্রয় করে। প্রাচীন ভারতেও পর্ব্বতদের একসময় দুটো করে পক্ষ বা ডানা গজায়। আদিম সাম্যবাদ থেকে আদিম সমাজতন্ত্রে অধঃপতিত হবার পর ঐ ‘পর্ব্বত’গুলির সৃষ্টি হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন ব্যক্তিমালিকানার বিকাশ ঘটে, ব্যবসায়ীরা ঐ ‘পক্ষ’গুলির কাছে সরাসরি কেনাবেচা শুরু করে। তাই কাহিনী এইরূপ যে ইন্দ্রস্ত্রী (Industry)-পতি ইন্দ্র ঐসকল পর্ব্বতের ডানা কেটে দেন। বাৎস্যায়নের মত সংস্থার আবির্ভাব সেইরূপ পর্ব্বতেরই উত্তরাধিকার।
টীকা—
১২। এই বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে লেখকের ‘দিশা থেকে বিদিশায় – নতুন শতাব্দীর প্রবেশ বার্ত্তা’ গ্রন্থের অন্তর্গত “লক্ষ্মীর পাঁচালী : ওয়েলফেয়ার ইকনমির ভূত ভবিষ্যৎ” শীর্ষক নিবন্ধে।
বৎস্যবৃদ্ধির চিন্তাই যেহেতু বাৎস্যায়নের অস্তিত্বের ভিত্তি, তার কামসূত্র গ্রন্থটিতে উৎপাদনশীল কাজকর্ম্মে লিপ্ত হবার সূত্রগুলি একে একে পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ধরনের উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞে পরিচালক (পুরুষ) ও কর্ম্মিগণ (স্ত্রী) কীভাবে কর্ম্মরত হবে, সে সকল বিষয়ে নির্দ্দেশ উপদেশগুলি জানতে পারা যায়। চুক্তির আগে পরিচালক ও কর্ম্মিগণের করণীয়, চুক্তি করার পদ্ধতি, চুক্তি রূপায়ণ, ইত্যাদি ম্যানেজমেণ্ট ও লেবার-ল’ সংক্রান্ত বহু তথ্যই তাতে আলোচনা করা হয়েছে। তবে যেহেতু বাৎস্যায়নের কাল বৈদিক যুগের সূত্রপাত থেকে অনেক পরে, এতে আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী কিঞ্চিৎ ক্ষীণকায় হয়ে এসেছে এবং দেহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী সবে তার শৈশবে পা রেখেছে। বস্তুত বাৎস্যায়নের যুগ হল ‘অবস্থান্তর প্রাপ্তির যুগ’। তাই তার কামসূত্রে সমাজদেহের কামচর্চ্চা ও মানবদেহের কামচর্চ্চা একই বর্ণনায় না সেরে কোথাও কোথাও পৃথক বর্ণনায় সারা হয়েছে। মোট কথা, এই গ্রন্থে বহুরৈখিক বর্ণনা একরৈখিক বর্ণনায় পর্য্যবসিত হয়েছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে। কারণ, বাৎস্যায়নের নিকট থেকে ঐ কামসূত্র বা কামকাজের নিয়মাবলী যখন আমরা পাচ্ছি, ততদিনে ভারতসমাজের বিস্তর বদল ও বিবর্ত্তন ঘটে যায়। সেই বিবর্ত্তন কতখানি তার বর্ণনা বাৎস্যায়নের নিকট থেকেই শোনা যাক।
“যে সকল আচার্য্য ধর্ম্মাদির আচার নিজে করিয়াছেন, পরকে ব্যবহার করাইয়াছেন এবং তাহার সঞ্চয় করিয়া গ্রন্থাকারে আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল আচার্য্যকে নমস্কার। সেইজন্য এই শাস্ত্রে তাঁহাদিগের সম্বন্ধ আছে। আগম প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, প্রজাপতি আদিকবি ব্রহ্মা প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের স্থিতিনিবন্ধনের জন্য প্রথমে একলক্ষ অধ্যায়াত্মক ত্রিবর্গসাধন (ধর্ম্ম-অর্থ-কাম সাধন) বিশদভাবে বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে— কামশাস্ত্রকে পৃথক করিয়া এক সহস্র অধ্যায়ে বিশদভাবে বলিয়াছিলেন মহাদেবের অনুচর নন্দী। ঔদ্দালকি শ্বেতকেতু তাহাই পাঁচশত অধ্যায় দ্বারা সংক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন। তাহাই আবার পাঞ্চাল দেশীয় বভ্রুপুত্র বাভ্রব্য একশত পঞ্চাশ অধ্যায়ে কন্যাসম্প্রযুক্তক, ভার্য্যাধিকারিক, বৈশিক, পারদারিক, সাম্প্রয়োগিক ও ঔপনিষদিক— এই সাত অধিকরণে বিভাগপূর্ব্বক সংক্ষেপে একখানি সংগ্রহগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার ঐ বৈশিক অধিকরণকে— করিয়াছিলেন। এইরূপভাবে বহু আচার্য্য সেই বাভ্রব্য সংগৃহীত শাস্ত্রের এক এক ভাগ অবলম্বন করিয়া খণ্ড খণ্ড আকারে প্রণয়ন করিতে থাকিলে, বাভ্রব্যোক্ত শাস্ত্রের কিছু কিছু করিয়া অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে প্রায় উৎসন্ন হইয়াছিল। তার মধ্যে দত্তকাদি প্রণীত গ্রন্থ সেই শাস্ত্রের এক একটি অবয়ব বলিয়া একদেশ বিধায় এবং বাভ্রবীয় শাস্ত্র অতীব বিশাল আয়তন বলিয়া অধ্যয়নের দুঃখকরত্ব বিধায়, সংক্ষেপে সমস্ত বিষয় অল্পগ্রন্থ দ্বারা কামসূত্র আমি প্রণয়ন করিয়াছি”। — বাৎস্যায়ন।
কামসূত্র গ্রন্থটির উত্তরাধিকার সম্পর্কে এই হল বাৎস্যায়নের বিবরণ। অর্থাৎ, আদিম সাম্যবাদী সমাজের শেষ পাদে জ্ঞানজীবীদের যে আদি সঙ্গঠন (ব্রহ্মা) গড়ে ওঠেছিল, তার থেকে শুরু করে, বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত যত জ্ঞানী গুণী মনীষীরা এই বিষয়ে চর্চ্চা করেছেন, তাঁদের সকলের কথার কিছু না কিছু এই গ্রন্থে পাচ্ছি। এর পর আবার এই বাৎসায়নের কামসূত্র গ্রন্থটি কী কী উপায়ে আজ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীযুক্ত মহেশ্চন্দ্র পাল মহাশয়ের সম্পাদনায় গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগরের বঙ্গানুবাদের বর্ত্তমান সংস্করণটিতেই পাওয়া যায়।
কামসূত্রের এই সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক যাত্রাপথের আদি থেকে অন্তিমে পৌঁছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বহু অর্থবাচক কামসূত্র অর্থকরী দিক থেকে হাল্কা হতে হতে ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত একার্থবাচক হয়ে গেছে। বলতে গেলে আদিতে যা ছিল জ্ঞানী-কর্ম্মীর মধ্যেকার সম্পর্কের সূত্রাবলী, অন্তিমে তাই মানব-মানবীর মধ্যেকার সম্পর্কসূত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে। তবে বাৎস্যায়নের কালখণ্ডটি যেহেতু ‘অবস্থান্তর প্রাপ্তির যুগ’, তাঁর রচিত কামসূত্রের ভিতর অতীতের ধ্যান-ধারণার বেশ কিছু অংশকে আমরা সজীব পেয়ে যাই। তবে বহুরৈখিকতার থেকে ভারতীয় ভাষা দৃষ্টিভঙ্গীর যে ক্রমাগ্রগতি (বা ক্রমাধঃপতন), যা কিনা সনাতন যুগ থেকে বৈদিক-বৌদ্ধ-হিন্দু-মোগল যুগ পেরিয়ে ব্রিটিশের ভারত অধিকারের পর সম্পূর্ণ হয়েছে, সেই ক্রমাগ্রগতি কার্য্যত কামসূত্রের সমাজ দেহ বিষয়ক ভাবনাকে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও কোথাও মানবদেহ বিষয়ক ভাবনায় অধঃপতিত করে ছেড়েছে। একথা প্রায় সকল প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের ক্ষেত্রে কমবেশী প্রযোজ্য। এই সেই কারণ, যেজন্য ভারতীয় কামশাস্ত্রকে কেবলমাত্র Sexology-র গ্রন্থ বলে ভ্রম হয়। সন্তান উৎপাদন ও পণ্য উৎপাদন, সব উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পর্ককে একই তত্ত্বের মধ্যে বেঁধে বর্ণনা করাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় রীতি।
কিন্তু আত্মাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বহুরৈখিক ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাবোধ খুইয়ে আমরা তাকে কেবল সন্তান উৎপাদনের তত্ত্ব বলে বুঝেছি এতকাল। মাঝ থেকে, পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত বিধি (করণীয়) নিষেধ (অকরণীয়) গুলিকে সন্তান উৎপাদন সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ বলে ভারতীয়রা মান্য করে চলেছে। এ দেশে দাম্পত্যজীবনের বহু বিড়ম্বনার উৎস এখানেই।
তবে বাৎস্যায়নের কামসূত্র পাঠের আগে যে সকল শব্দ ব্যবহার করে গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে, সেগুলির অন্তত দু’একটিকে একটু নাড়াচাড়া করে শব্দগুলির স্বভাব চরিত্র কীরূপ এবং সেগুলিতে আমাদের কীরূপ অধিকার তা জানলে বা বুঝলে, আমরা ঐ বিড়ম্বনার ভাষাতাত্ত্বিক উৎসটিকে চিনতে পারব।
পতিব্রতা = পতির (মালিকের) ব্রতই (Planning & Programming) যার ব্রত। মালিক বা পরিচালক যা চায়, যে ঠিক সেই রকমটাই করে, তেমন কর্ম্মীই পতিব্রতা। কামিনী = কামিন্, মজুর। মেয়ে দিনমজুরদের মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে ‘কামিন্’ বলা হয়।
পরিণয় = < পরিণমন > পরিণাম = ‘প্রস্তুত প্রয়োজনের সাধনরূপে প্রসিদ্ধ বস্তু আরোপ বিষয়ের সহিত অভেদ ভাবে পরিণত হইয়া প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী হইলে পরিণাম হয়’। পরিণামদর্শী = ‘কর্ম্মের ফল যিনি দেখতে পান’। ত্রিকালদর্শী = বস্তু আগে কেমন ছিল, এখন কীরূপে আছে, ভবিষ্যতে কীরূপ বস্তুতে পরিণত হবে – বস্তুর এই তিনকাল যিনি দেখতে পান। ‘প্রস্তুত (প্রস্তাবিত) প্রয়োজনের সাধনরূপে প্রসিদ্ধ বস্তু’ = কাঁচামাল। ‘আরোপ বিষয়ের সহিত অভেদ ভাবে পরিণত হইয়া’ = ‘Know how’-যুক্ত শ্রম নিষিক্ত হইয়া। ‘প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী হইলে পরিণাম হয়’ = product হয়।
এ তালিকা দীর্ঘ করার উপায় নেই, একটা আন্দাজ দেওয়া গেল মাত্র, এখন বাৎস্যায়নের কামসূত্র থেকে কয়েকটি বাক্য পেশ করা যাক, যেগুলি আমাদেরকে ম্যানেজমেণ্ট ও লেবার-ল’ সংক্রান্ত কিছু প্রাচীন তথ্য সরবরাহ করে।
১. ‘‘স্পর্শ বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া আভিমানিক সুখে অনুবিদ্ধ ফলবান বিষয়বোধই প্রধান কাম’ ১২/২৮ [স্পর্শ < স্পৃশ্ = আমর্শন = পরামর্শ, মন্ত্রণা] স্মর্তব্য যে আদিতে ‘স্পর্শ হইতে সন্তান উৎপাদন হইত’, বিবাহের প্রয়োজন ছিল না।
২. ‘কামসূত্রের অধ্যয়ন বা নাগরিকজনের সমবায় হইতে সেই কাজের বিষয় জানিয়া লইবে’। ১৩/২৯
৩. ‘আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন— তির্য্যগ যোনিতেও [‘যাহাদের আহার সঞ্চার তির্য্যগ’ অর্থাৎ বাঁকা। অর্থাৎ কিনা প্রচলিত সমাজনীতি অনুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ না করে যারা বাঁকা পথ ধরে’। নিম্ন-অধিকারিগণ এই শব্দের অর্থ করে ‘পশুপাখী’। ফল যতখানি হাস্যকর হওয়া সম্ভব তাই হয়]। কাম স্বয়ংই প্রবৃত্ত হয় এবং উহা আত্মার একটি নিত্য ধর্ম্ম; সুতরাং কামাববোধার্থ শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই’। ১৭/৩১
৪. ‘পুরুষ [executive]ধর্ম্মবিদ্যা অর্থবিদ্যা ও অঙ্গবিদ্যার কাল অনুরোধ না করিয়া কামসূত্র ও তাহার অঙ্গবিদ্যার অধ্যয়ন করিবে’। ১/৫২
৫. ‘অভ্যাস ও প্রয়োগের যোগ্য চাতুঃষষ্টিক যোগ [যার মধ্যে Engineering, mining, metallurgy] সবই পড়ে] কন্যা নির্জ্জন প্রদেশে একাকিনী বসিয়া নিজে নিজেই অভ্যাস করিবে’। ১২/৫৬
৬. কর্ম্মীসংগ্রহ বিষয়ে মতামত— ‘চতুঃষষ্টি কলায় বিচক্ষণ ব্যক্তি কন্যাগণ কর্ত্তৃক অনুরাগত বীক্ষমান হইলেও সমাগম ব্যতীত সম্প্রয়োগ হয় না; এই জন্য তাহার সমাগমোপায় — আবার বলা যাইতেছে। যে উপায় অবলম্বন করিলে স্ত্রী সমাগম লাভ করা যায় তাহাকে আবাপ বীজবিকিরণ বলে। তাহার মধ্যে উদ্বাপ [সমাগমলাভের শ্রুয়মান বৈধ ও অবৈধ উপায়] আটটি বিবাহ …’। এই বক্তব্য বাৎস্যায়নের কামসূত্রের টীকাকারের।
৭. বাৎস্যায়ন বলেন— ‘অর্থলাভ, অনর্থপ্রতিঘাত এবং প্রীতিই অভিগমনের কারণ। প্রীতিদ্বারা অর্থের বাধ হইতে পারে না; কারণ অর্থেরই প্রাধান্য’। ৯/১৯৪
৮. অন্যের কর্ম্মীবাহিনীকে দিয়ে নিজের কার্য্যোদ্ধার করার উপায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে ‘পরদারে গমন করিতে হইলে প্রথমএইগুলির পরীক্ষা করিবে— সাধনের যোগ্য কি না, নিরাপদ কি না, সেটি আয়তিকর [গৌরবজনক] কি না এবং তদ্বারা বৃত্তিলাভ সম্ভবপর কি না’। ২/২৫০
৯. কর্ম্মীদের ওপর কীভাবে administration চালানো হবে, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, — ‘শব্দাদি(?) বিষয় অবলম্বন করিয়া কর্ম্মের বারংবার অনুষ্ঠানবশত যে প্রীতি বহির্ম্মুখী হয়, তাহাকে আভ্যাসিকী প্রীতি কহে। যেমন মৃগয়াদি কর্ম্মের বারংবার অনুষ্ঠানে সুখলাভ হইয়া থাকে’। ৩৭/৩২৯
১০. ‘শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট এইসকল প্রীতিকে শাস্ত্রানুসারে বিবেচনা করিয়া, তাহাকে সেইভাবেই প্রবর্ত্তিত করিবে’। ৪১/৩৩০
১১. ‘পূর্ব্বাচার্য্যগণ সম্প্রয়োগের অঙ্গ চতুঃষষ্টি (৬৪) প্রকার বলিয়া থাকেন; কারণ সম্প্রয়োগই চতুঃষষ্টি (৬৪) প্রকারময়। … দশমণ্ডলাত্মক ঋকে দশাবয়ব সম্প্রয়োগ যে চতুঃষষ্টি, ইহা নাম করিয়া বলা হইয়াছে’।
যাই হোক, কামসূত্রের যে সারকথা, মানব-মানবী রাজা-প্রজা পুরুষ-প্রকৃতি জ্ঞানী-কর্ম্মী পরিচালক-পরিচালিত সকলের কাম চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে যে কথাটি প্রযোজ্য, এখন সে কথাটি উল্লেখ করা যাক— ‘যেখানে পরস্পর পরস্পরের সুখের অনুভব করিয়া আনন্দক্রীড়ায় নিমগ্ন হয়, পরস্পর পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, সেখানে সেই সম্বন্ধই প্রশস্ত’। ২০/১২৬। আধুনিক ম্যানেজমেণ্ট তত্ত্ববিশারদগণ, যাঁরা পুনরায় কর্ম্মিজনগণের মধ্যে কর্ম্মোন্মাদনা জোগানোর চেষ্টা করছেন অর্থাৎ মদনকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন work-culture ইত্যাদি নামে, তাঁরা কামসূত্রের এই বাক্যটিতে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করলে বহু সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবেন, আশা করা যায়। তাহলেই তাঁরা মদন বাঁচিয়ে তোলার পথ পেতে পারেন। আর মদনকে না বাঁচিয়ে আধুনিক বিশ্বের পরিত্রাণ নেই।
শেষ কথা এই যে, বলা হয়েছে— জগতের যা কিছু অহিত তার কারণ হল পুরুষপ্রকৃতির মধ্যে ‘ভোগ্যা-ভোক্তৃ’ সম্পর্ক সৃষ্টি। রাজা-প্রজা, জ্ঞানী-কর্ম্মী, পরিচালক-পরিচালিত, জীব-জড়, এই যে পুরুষ-প্রকৃতির নানা রূপ, এদের মধ্যেকার স্বাভাবিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়ে ‘ভোগ্যা-ভোক্তৃ’ সম্পর্ক হয়ে গেছে। পুরুষ ভোগ করছে, প্রকৃতি ভুক্ত হচ্ছে। বলা হয়েছে— এমনটা হওয়া সভব হয়েছে ‘অবিদ্যা’ বা ‘অবিবেকের’ জন্য। তবে কপিলের সাংখ্যে নিদান দেওয়া হয়েছে যে, যে কারণেই ঐরূপ ‘ভোগ্যা-ভোক্তৃ’ সম্পর্ক সৃষ্টি হোক না কেন, তাহার উচ্ছেদই পুরুষার্থ।
‘… তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থ’।
উপসংহার—
কেবল বাৎস্যায়নের কামসূত্রই নয়, আমাদের সমগ্র প্রাগাধুনিক ডিসকোর্সই যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থেকে গেছে। সেখান থেকে আমাদের আধুনিক ডিসকোর্স গড়ে উঠবার সুযোগই পেল না। তার আগেই, আমাদের ঐ প্রাগাধুনিক ডিসকোসের দেহে ইউরোপের আধুনিক ডিসকোর্সের আত্মা ঢুকে পড়ে জন্ম দিয়েছে এক ঔপনিবেশিক দোআঁশলা ডিসকোর্সের। এখন আমরা তাতেই অভ্যস্ত আছি। এখান থেকে আমাদের বেরুতে হবে, তবে পেছন দিকে হেঁটে নয়; সামনে এগিয়ে। অতীতের অর্জ্জনগুলিকে রহস্যমুক্ত করে সংগ্রহ করে নিয়ে, বর্ত্তমান প্রাপ্তিগুলিকে তার সঙ্গে মিলিয়ে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করে গুছিয়ে নিয়ে, আমাদেরকে সামনে পা ফেলে হেঁটে যেতে হবে।
[‘‘ভাষায় ঔপনিবেশিকতা : প্রাচীন ভারতে ম্যানেজমেণ্ট ও বাৎস্যায়নের কামসূত্র’’ নিবন্ধটি ‘দিশা থেকে বিদিশায় : নতুন সহস্রাব্দের প্রবেশবার্ত্তা (১৯৯৯)’ গ্রন্থ থেকে পুনঃপ্রকাশ করা হল …
এবং নিবন্ধটির পুনরায় বানান সম্পাদনা করেন ভাষাতাত্ত্বিক শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দাস।
— চারবাক সম্পাদকীয় ]
ছবির উৎস : রুদ্র শায়ক
কলিম খান
জন্ম: ০১ জানুয়ারী ১৯৫০ মামুদাবাদ (মেদিনীপুর)। মৃত্যু: ১১ জুন ২০১৮ কলিকেতা।কলিম খানের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী:
১. মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে (১৯৯৫)
২. দিশা থেকে বিদিশায় : নতুন সহস্রাব্দের প্রবেশবার্ত্তা (১৯৯৯)
৩. জ্যোতি থেকে মমতায় : ফ্রম এনলাইটেনমেন্ট টু…. (২০০০)
৪. পরমাভাষার সংকেত (২০০১)
৫. আত্নহত্যা থেকে গণহত্যা : আসমানদারী করতে দেব কাকে (২০০২)
৬. পরমা ভাষার বোধন উদ্বোধন : ভাষাবিজ্ঞানের ক্রিয়াভিত্তিক রি-ইঞ্জিনিয়ারিং (২০০২)কলিম খান ও রবি চক্রবর্ত্তীর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী:
১. বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ (২০০৬)
২. অবিকল্পসন্ধান : বাংলা থেকে বিশ্বে (২০০৮)
৩. বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ, ১ম খণ্ড (২০০৯) ও বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ, ২য় খণ্ড (২০১১)
৪. সুন্দর হে সুন্দর (২০১১)
৫. বঙ্গযান (২০১২)
৬. সরল শব্দার্থকোষ (২০১৩)
৭. বাংলা বাঁচলে সভ্যতা বাঁচবে (২০১৩)
৮. বঙ্গতীর্থে মুক্তিস্নান : বাংলাভাষা থেকে সভ্যতার ভবিতব্যে (২০১৫)
৯. ভাষাই পরম আলো (২০১৭)